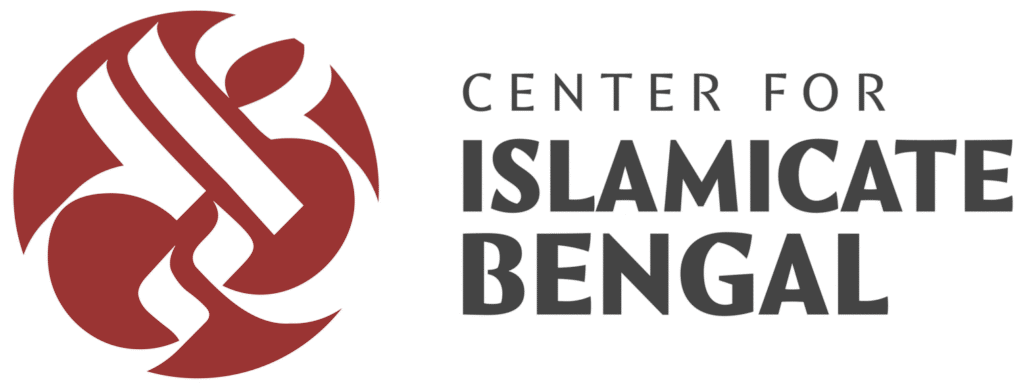একটা মুখরোচক গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। গল্পটা খুবই প্রচলিত, যে রবার্ট ক্লাইভ নাকি লন্ডনে গিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন। তিনি দাবি করেন, আমরা যখন মুর্শিদাবাদের রাস্তায় নামি, তখন রাস্তার দুই পাশে জনতার ভিড়। তারা যদি আমাদের দিকে পাথর ছুড়ে মারত, তাহলেও আমাদের পক্ষে বাংলা জয় করা সম্ভব হতো না। কথাটা মুখরোচক। যদিও সত্য-মিথ্যা আমরা জানি না। কিন্তু এর দ্বারা একটা বিষয় স্পষ্ট হয়। সেটা হলো রাস্তার দুই ধারে থাকা মানুষেরা রাজনৈতিকভাবে প্রায় নন-এক্সিস্টেন্ট। এই অস্তিত্বহীন মানুষগুলো কীভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিল বা শতাব্দীর ব্যবধানে তারা কীভাবে জনতা হয়ে হাজির হলো; তার ব্যাখ্যাটা বোধহয় সে অর্থে আলোচনা করা হয় না।
গণতন্ত্রের আলোচনায় আসলে সবার আগেই ধরে নেয়া হয় যে, গণতন্ত্র ইউরোপীয়। আমরা যে বিদ্যমান যে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির কথা বলি, তা ইউরোপীয় বটে। কিন্তু অ্যাথেনিয়ান ডেমোক্রেসির মতো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন সময়ে ডেমোক্রেসি ছিল, যাকে প্রোটো-ডেমোক্রেসি বলা হয়। বাংলায় ইতিহাসে পাল বংশের শাসক গোপালের নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছিল। ইসলামের ইতিহাসে রাসূল (সা.)-এর পরে যে খলিফাগণ নির্বাচিত হয়েছেন, তার তো কোনো পদ্ধতিগত উপায় ছিল না। প্রত্যেকটা খলিফা নির্বাচন আসলে আলাদা প্রক্রিয়ায় হয়েছে। সেখানে ডেমোক্রেটিক উপাদান ছিল। ধ্রুপদি মুসলিম জ্ঞানচর্চায় মুতাজিলা ও খারেজিরা দাবি করেছেন, রাষ্ট্রের শাসক একজন না হয়ে একটা অ্যাসেম্বলি বা নির্বাচিত দল হতে পারে। তার মানে এসবকে গণতন্ত্রের প্রস্তুতি-পর্ব হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়। যখন ইউরোপের গণতান্ত্রিক উপাদান এশিয়ান দেশগুলোতে প্রবেশ করছে, তখন সে দেশগুলোর মধ্যে আগে থেকে বিদ্যমান কিছু অনুকূল বৈশিষ্টে্যর কারণেই সফল হয়েছে।
আধুনিক সময়ে গণতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ বিশ্বায়ন। এর মধ্য দিয়ে মুসলিম-অধ্যুষিত যে অঞ্চলগুলো ছিল, তাদের মধ্যে একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিশেষ করে উনবিংশ এবং বিংশ শতকে। বিশেষ করে ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং বাংলা অঞ্চল পর্যালোচনা করলে আমরা একটা কমন প্যাটার্ন পাই। দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক চর্চার দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। এ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তারা প্রথমে তারা পত্রিকা প্রকাশ করেছে, সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে, তারপরে তারা শাসকের ক্ষমতা কমিয়ে এনেছে, জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। এই প্যাটার্নটা সব জায়গায় দেখা যায়। মিসরের কথা ধরা যাক। মিসরে তখন উনবিংশ শতক। বেশ কিছু পত্রিকা দাঁড়িয়েছে। Egypt for Egyptians- এই স্লোগান সামনে নিয়ে দাঁড়িয়েছে জাতীয়তাবাদ। ‘আল আহরাম’-এর মতো পত্রিকাগুলো পাবলিক স্পিয়ার তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। তুরস্কে তানজিমাত নামে একটা সংস্কার আন্দোলন হয়েছে উনবিংশ শতকে। এই সংস্কারের মধ্য দিয়ে সুলতানের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে, নাগরিক অধিকারের সমুন্নত করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে যে ধর্মীয় বিভেদ ছিল, সেটাকেও সমতার পর্যায়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। একইভাবে ইরানে দেখছি, ইরানে ১৯০৬ সালের দিকে কনস্টিটিউশনাল রেভলিউশন হয়। এর মধ্যে দিয়ে শাহের ক্ষমতা হ্রাস পায়। মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। ঠিক এই সময়টাই কিন্তু আবার বাংলায় ঢাকায় তখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। একই সময়ে ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সারেকাতে ইসলাম। বৈশ্বিক মুসলিম জনগোষ্ঠী যেভাবে বিশ্বায়ন, জাতীয়তাবাদ এবং ইউরোপীয় আধিপত্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তারই অংশ হিসেবে আমরা বাংলার প্রতিক্রিয়া পাঠ করতে পারি। এটা করলে পাঠটা তুলনামূলক সহজ হয়।
বাংলায় বাঙালি মুসলমানের গণতান্ত্রিক যাত্রাটাকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথমটা হচ্ছে তাদের মধ্যে পাবলিক স্ফিয়ার তৈরি। এইটা ১৮৫৫ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত। এরপর ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত সময়টাকে আমরা রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ হিসেবে আখ্যা দেব। ১৯১২ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সময়টাকে আমরা বলব রাজনৈতিক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মেরুকরণের মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই অংশটাকে আমরা আলাদাভাবে জোর দিয়ে দেখতে চাই। সবিশেষ ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়টা আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে গণতন্ত্র বিকাশের যোগ। এই সময় মন্ত্রিসভা গঠন হচ্ছে এবং বাঙালি মুসলমানরা ক্ষমতার কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করছে।
বাংলার রেনেসাঁর ঘটনায় এবার একটু ফিরে যেতে হবে। বাঙালি মুসলমানের জাগরণকে সনাক্ত করতে চাইলে বাঙালি হিন্দুর জাগরণকেও সনাক্ত করতে হবে। কারণ বাঙালি হিন্দুর যে জাগরণ, যেটাকে আমরা বেঙ্গল রেনেসাঁ বলি, সেটা বেদান্তিক হিন্দু পরিচয়কে সামনে এনেছে। বাঙালি রেনেসাঁ বলতে তারা মূলত বাঙালি হিন্দুর রেনেসাঁকেই বোঝান। সমকালীন বাঙালি বলতে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে চন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রায় সবাই বাঙালি হিন্দুকে বুঝিয়েছেন। বাঙালি রেনেসাঁ বলতে যে বাঙালি হিন্দু রেনেসাঁকে বুঝানো হতো, তার বড় প্রমাণ রামমোহন রায়ের রচনা। তার রচনা হিন্দু সমাজ সংস্কারকে ঘিরে। এইসব রচনায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এ কারণে এটা সহজেই বলা যায় যে, বেঙ্গল রেনেসাঁয় এক ধরনের ডি-ইসলামাইজেশন প্রক্রিয়া কার্যকর ছিল। এই ডি-ইসলামাইজেশনের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের ভাষার জগতে প্রভাব পড়ে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং হিন্দু কলেজের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত-বহুল বাংলা জনপ্রিয় হয়; লিটারেচারের মধ্যেও এই প্রবণতা আসে। এর ফলে বাঙালি মুসলমানের ভাষিক জায়গা সংকুচিত হতে থাকে। এ জায়গাটাই বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র পরিচয় গঠনের ক্ষেত্র তৈরি করেছে।
১৮৫৫ সালে প্রথম আঞ্জুমানে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সালটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলছি এই কারণে যে মুসলমানরা এই সময় আনুষ্ঠানিকভাবে সভা-সমিতির দিকে এগিয়ে আসে। আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন নওয়াব আব্দুল লতিফ। এই নওয়াব আব্দুল লতিফ পরবর্তীতে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির পর আমরা বাংলায় অজস্র সভা-সমিতি উদ্ভূত হতে দেখি। দুইটা ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। একটি ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে, আরেকটি মুসলমানদের পক্ষ থেকে। এই সময়ে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যে শিক্ষিত শ্রেণী উত্থিত হচ্ছিল, তারা বুঝতে পারছিল যে সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। এই পর্যায়ে মাওলানা আব্দুল লতিফ বড় একটি কাজ করছিলেন। মাওলানা আব্দুল লতিফের পাশাপাশি ছিলেন কারামত আলী জৈনপুরী। তিনি একজন সুফি। পড়াশোনা করেছিলেন শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী এবং শাহ ইসমাইল দেহলভীর কাছে। এই শিক্ষাগত পটভূমি তার উপর গভীর প্রভাব ফেলে। কারামত আলী জৈনপুরী কলকাতায় এসে ঘোষণা দিলেন, ফতোয়া দিলেন, যে ভারতবর্ষ দারুল হারব নয়, বরং দারুল ইসলাম। এই ফতোয়ার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি এইভাবে যে মুসলমান সমাজে প্রায় একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতবর্ষ দারুল হারব না দারুল ইসলাম; এ নিয়ে একটা বিতর্ক ছিল। ফরাজি আন্দোলন, তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া ও তিতুমীরের আন্দোলনের ভিতরেই ভারতবর্ষকে দারুল হারব হিসেবে দেখার প্রবণতা ছিল। সুতরাং যখন কারামত আলী জৈনপুরী বললেন ভারতবর্ষ দারুল হারব নয় বরং দারুল ইসলাম, এই ফতোয়ার পর বাংলাজুড়ে বড় প্রচারণা শুরু হয়। নতুন করে জুমা পড়তে হবে, নতুনভাবে ধর্মীয় আচার পালন করা হতে থাকে। এই ধারাটাই পরে তাইয়ুনি নামে পরিচিত হলো। এর পর মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তারা ভাবতে থাকে, কৌশলগত সহযোগিতা দরকার, যাতে নিজেদের অধিকারগুলো আদায় করা সম্ভব হয়।
ঠিক আরেকটা ঘটনা ঘটে এসময়। সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) দমন করার পর ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা নিয়ে ঘোষণা দেয় যে তারা এখন থেকে দেশীয়দের মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব নেবে। পূর্ববর্তী সম্প্রসারণ নীতি থেকে সরে আসবে। এই ঘোষণার ফলে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের নতুন আশা তৈরি হয়, যদি আমরা ব্রিটিশদের সঙ্গে বার্গেইন করি, তাহলে হয়তো আমাদের অধিকার আদায় করা সম্ভব হবে। এই দুইটা ঘটনা মিলেই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বড় ধরনের শিফট তৈরি করে। তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে কোঅপারেট করার মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ের চিন্তায় এগিয়ে যায়।
সৈয়দ আমীর আলীর সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন এবং নওয়াব আব্দুল লতিফের মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি সংগঠনের মধ্যে একটি সিগনিফিকেন্ট পার্থক্য ছিল। নওয়াব আব্দুল লতিফ ছিলেন পুরাতন এলিট শ্রেণীর প্রতিনিধি; তার অনুসারীরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণী ও রক্ষণশীল। তারা উর্দুর পক্ষপাতী ছিলেন; অন্যদিকে জনপ্রিয় স্তরের মানুষ বাংলা ও ইংরেজির দিকে ঝুঁকতেন। কিন্তু সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তার অনুসারীরাও আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান। ফলে আমীর আলীর পরিসর নওয়াব আব্দুল লতিফের পরিসরের তুলনায় অনেক বিস্তৃত ছিল। নওয়াব আব্দুল লতিফের সংগঠন ছিল বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমীর আলীর প্রভাব ছিল আরো ব্যাপক। কিন্তু সৈয়দ আমীর আলী বাংলার বাইরে গিয়ে একটি বিশাল পরিসরে বিস্তৃত হয়েছিলেন। আমরা যদি হিসেব করি, ১৮৭৮ সালে সেন্ট্রাল মোহামেডান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়, এবং ১৯০৫ সালের আগে এই সংগঠনের শাখার সংখ্যা ছিল আশিরও বেশি। পরবর্তী সংগঠনগুলোর মধ্যে ১৮৮৩ সালে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মীলন নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ১৮৮৪ সালে রাজশাহীতে নুর আল ইমান সমাজ, ১৮৮৮ সালে সাতক্ষীরায় মুসলমান সুহৃদ সম্মীলনী, যশোরে এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা, টাঙ্গাইলে আঞ্জুমানে মইনুল ইসলাম, রংপুরে নুরুল ইমান জামায়াত, নোয়াখালীতে আঞ্জুমানে আশায়াতে এসলাম, ত্রিপুরায় ত্রিপুরা হিতবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সবগুলোই উনিশ শতকের শেষদিকে। একই সময়ে চট্টগ্রামে ১৮৯৯ সালে মোসলমান শিক্ষা সভা এবং ১৯০২ সালে মুসলিম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও ছিল বহুমাত্রিক। কেউ শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে, কেউ সংস্কৃতি নিয়ে, কেউ অর্থনীতি নিয়ে, এমনকি কেউ খেলাধুলা নিয়েও কাজ করছে।
এই সময় শত শত পত্রিকাও প্রকাশ পায়। মিহির ও সুধাকর, ইসলাম দর্শন এবং আখবারে মোহাম্মদীর মতো এমন অজস্র পত্রিকা। এসব পত্রিকা এবং সমিতিগুলো মুসলমানদের প্রয়োজন, সমস্যা ও দাবি নিয়ে আলোচনা করতো। পরবর্তীতে এগুলোর মধ্য থেকে নির্বাচিত সমস্যাগুলো ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে উপস্থাপন করা হতো। সৈয়দ আমীর আলী লর্ড লিটনের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। লর্ড রিপন পরবর্তীতে ব্রিটিশ পলিসিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। এই অংশটি ছিল প্রথম পর্বের সমাপ্তি।
দ্বিতীয় অংশে আমরা বলছি রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের সময়কাল ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত। এই সময় বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। বুঝা দরকার কেন কংগ্রেস থাকা সত্ত্বেও ভারতে আরেকটি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন; মুসলিম লীগ কেন প্রয়োজন হয়ে পড়ল? ব্যাপারটা এমন নয় যে মুসলিম লীগ হঠাৎ করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু করল। এর পেছনে একটি জরুরি দলিল আছে। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের মোট সদস্যের মাত্র ১০ শতাংশ মুসলমান ছিল। প্রথম অধিবেশনে ৭২ জন সদস্যের মধ্যে মুসলমান ছিলেন মাত্র দুইজন। সেই সময় স্টেটসম্যান পত্রিকায়ও মন্তব্য এসেছিল যে মুসলমানদের জাতি হিসেবে কংগ্রেসের মূল রাজনীতির বাইরে রাখা হচ্ছে। এই কারণে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই মুসলমানদের মধ্যে নানা মতবিরোধ দেখা যায়। যেমন সৈয়দ আমীর আলীর সঙ্গে নওয়াব আব্দুল লতিফের বিরোধ ছিল; এবং স্যার সৈয়দ আহমদের সঙ্গে আব্দুল লতিফের মিলতো না।
কিন্তু তারা এক বিষয়ে সবাই একমত ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ মেলানো সম্ভব নয়। কারণ কংগ্রেস মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছিল না। তাই মুসলমানদের জন্য আলাদা রাজনৈতিক পাটাতন থাকা উচিত। এটা তারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিল। পরবর্তীতে কংগ্রেস থেকে যখন মুসলমান নেতাদের কাছে ইনভাইটেশন লেটার পাঠানো হয়, অনেকেই তা গ্রহণ করেননি। পালটা চিঠিতে তারা জানান যে কংগ্রেসকে তারা মুসলমানদের স্বার্থের যথার্থ প্রতিনিধি মনে করেন না। এই জায়গা থেকেই বঙ্গভঙ্গের প্রশ্ন উঠে আসে, এবং বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে যখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়, তখন বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের রায়ত সমাজ, কৃষক সমাজ এবং সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজ এটিকে অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে। বাঙালি মুসলমানরাও এর পক্ষে অবস্থান নেয়। কিন্তু একই ঘটনাকে হিন্দু সমাজ এবং কংগ্রেস সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলেই স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। স্বদেশী আন্দোলনের যে একটি অংশ আমরা প্রায়ই এড়িয়ে যাই তা হলো, স্বদেশী আন্দোলনের ভেতরে একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রকল্পের রূপরেখা তখনই স্পষ্টভাবে গঠিত হচ্ছিল। এই হিন্দু রাষ্ট্র প্রকল্পের উত্থানের কারণেই বাঙালি মুসলমানরা তৎকালীন জনমত, পত্রিকার ভাষ্য এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থান থেকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়নি। এর মূল কারণ ছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্ন। এটি বোঝার জন্য আমাদের ঐতিহাসিক পটভূমিটাও দেখতে হবে কিভাবে বঙ্কিমচন্দ্র, পরে চন্দ্রনাথ বসুর মাধ্যমে হিন্দু ন্যাশনালিজমের বিকাশ ঘটেছিল। এটি উনিশ শতকের শুরু থেকেই চলছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে যখন চন্দ্রনাথ বসু ১৮৯২ সালে ‘হিন্দুত্ব’ বইটি লেখেন—এই বইটি কিন্তু সাভারকার বা বাল গঙ্গাধর তিলকের বহু আগে লেখা। অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদের ধারণাটি বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবিতেই আগে গড়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটেই মুসলমান নেতৃত্ব বুঝতে পারে যে আলাদা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম দরকার।
তাই ১৮৯২, ১৮৯৮ বা ১৯০৫-এর আগের পুরো কনটেক্সটেই দেখা যাচ্ছে যে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের জন্য আলাদা রাজনৈতিক কাঠামোর প্রয়োজন ছিল। আরেকটি জরুরি তথ্য হলো- ১৯০৫ সালের আগস্টের দিকে, বঙ্গভঙ্গের বছরে, Sir J. Bampfylde Fuller পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ ছিল বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র প্রতিক্রিয়া। এই ঘটনার পর স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব আলী চৌধুরী এবং অন্যান্য মুসলিম নেতারা বাঙালি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি নতুন প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এখান থেকেই মুসলিম লীগের জন্ম। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা নয় বরং মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতার বৃদ্ধি।
পরবর্তী ১৯১২ সাল পর্যন্ত হিন্দু সমাজের একটি অংশ হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালাতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলন, শিবাজী উৎসবের জাতীয়করণ, হিন্দু মেলা উদযাপন এবং রাখীবন্ধন সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করছিল। বাঙালি মুসলমানরা এসব করতে পারেনি, ফলে তারা ক্রমশই রাজনৈতিকভাবে মার্জিনালাইজড হয়ে পড়ে। তবে এই সময় দুটি পজিটিভ ঘটনা ঘটে: ১৯০৬–এর পরে এলিট মুসলমান শ্রেণী গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে শুরু করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, রাজশাহী—সব জায়গাতেই এই সংযোগ গড়ে ওঠে। এটি গণতান্ত্রিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এলিটরা বুঝতে পারেন যে জনগণকে সঙ্গে না নিলে তারা রাজনৈতিকভাবে এগোতে পারবেন না। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানদের নির্দিষ্ট প্রতিনিধিত্ব এবং পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। এর মধ্য দিয়েই মুসলমানদের রাজনৈতিক পরিচয় ও গণ-অংশগ্রহণ একটি আনুষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করে। এইটা থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠীর তরফ থেকে প্রতিবাদ আসে। কিন্তু এইটা মুসলমানদের মধ্যে আরেক ধরনের চেতনা তৈরি করে যে তাদের প্রতিনিধিত্ব এখন নিশ্চিত হয়েছে, তো এই অনুপাতে তাদের প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়াতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে এই সময়ে নতুন আরেকটা শ্রেণী আসে, যেটা হচ্ছে এন্টি-লয়ারিস্ট। মুসলিম লীগ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার লাইন ছিল যে, তারা ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা করবে, আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং যে যে অধিকার দরকার তা আদায় করে নিয়ে আসবে। তো এই সময়ে সামনে আসে আমাদের শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, বর্ধমানের আবুল কাসেম এবং অন্যান্য যে ইয়াং লিডাররা, যারা আসলে ব্রিটিশ আনুগত্যকে মুখ্য হিসেবে দেখেন না। তারা দেখেন যে মুসলমানদের রাষ্ট্রিক অবস্থানটা কিভাবে শক্ত করা যায় এবং তারা এখানে কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করতে কমবেশি আগ্রহী। তো তারাই একটু সামনের দিকে চলে আসে এবং এই আশাটা প্রথমদিকে ভিজিবল হয় বঙ্গভঙ্গ রদের পর থেকে। কারণ বঙ্গভঙ্গ রদের পরে বাঙালি মুসলমানের যে রিপ্রেজেন্টেশন মর্লি–মিন্টো সংস্কারের মধ্য দিয়ে হচ্ছিল, তার মধ্যে একটা বড় ধাক্কা লাগে বাঙালি মুসলমানের জন্য।
বঙ্গভঙ্গ রদের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বড় ধরনের হতাশা তৈরি হয়। তারা বুঝতে পারে যে ব্রিটিশরা তাদের আসলে যা দিতে চাইছে বা যেভাবে দিচ্ছে, সেটা তাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটাচ্ছে না। এমনকি কংগ্রেসের সাথে তারা কোঅপারেট করলেও তারা ক্ষমতায়িত হবে না। তো এই যে পুরাতন যে নেতারা, তাদের কেউ কেউ ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যপ্রবণ হলেও আমরা তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখি। যেমন নওয়াব আলী চৌধুরী– যাকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশদের সাথে কো-অপারেশনের মধ্যেই দেখি– তিনি খেলাফত আন্দোলনের ইস্যুতে বাঙালি মুসলমানদের নেতৃত্ব হাতে নিয়ে নেন। ওদিকে নওয়াব আলী চৌধুরীর পাশে যোগ দেন হাবিবুল্লাহ। তিনি স্যার সলিমুল্লাহর ছেলে। এখন আমরা এই বাঙালি মুসলমানের ডেমোক্রেটিক জার্নির ক্ষেত্রে দেখি যে বিশ শতকের প্রথম দিকে সবচেয়ে বড় দুইটা পয়েন্ট ছিল: একটা হচ্ছে প্যান-ইসলামিজম এবং আরেকটা হচ্ছে খেলাফত আন্দোলন। খেলাফত আন্দোলন এবং প্যান-ইসলামের কারণে বাঙালি মুসলমান অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন হয়েছে নিজেদের ভূমি থেকে; তারা অনেক বেশি বাইরের সাথে, বৃহত্তর মুসলিম দুনিয়ার সাথে সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। এজন্য দেখা যায়, অটোমান সুলতানকে নিয়ে বাঙালি পত্রিকাগুলো লেখালেখি করছে। এই প্যান-ইসলামিজমকে মূলত রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে অন্তত ১৯২২ সাল পর্যন্ত। এই ১৯২২ সালের আগ পর্যন্ত মুসলমানরা যে খেলাফত আন্দোলনে আসে, এই খেলাফত আন্দোলনের মধ্যে বাঙালি মুসলমানের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল যে তারা অসহযোগ আন্দোলনের পাশে কংগ্রেসের সাথে কো-অপারেট করতে থাকে। এই কো-অপারেশনের মধ্য দিয়ে আইডিয়লজিক্যালি তাদের একটা গ্রাউন্ড কিছুটা শক্ত হয়, কিন্তু তাদের এই প্যান-ইসলামিজম এবং খেলাফত—এই দুইটা জিনিসই আবার তাদের মানুষ ও মাটি থেকে কিছুটা হলেও দূরে সরিয়ে দেয়।
এই সময় আমরা একটা উদাহরণ আনতে পারি, কেন আমি এটাকে ডেমোক্রেটিক জার্নির অংশ বলছি। খেলাফত আন্দোলনের সময় ত্রিপুরা থেকে কয়েকজন লোক সরাসরি জিহাদের ঘোষণা দিয়েছিল যে আমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। কিন্তু এই সময়ের পত্রিকাগুলো এবং আমাদের শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, বর্ধমানের আবুল কাসেমরা সরাসরি নিষেধ করেন। তারা বলেন, আমাদের খেলাফত আন্দোলন কোনভাবেই সহিংসতার দিকে যাবে না; এই আন্দোলনটা হবে অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ। আমরা অধিকার আদায় করব শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মধ্য দিয়েই। এই কারণেই দেখা যায়, অসহযোগ আন্দোলন যতটা সহিংস হয়ে উঠছিল সূর্য সেন বা ক্ষুদিরামদের মধ্য দিয়ে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে খেলাফত আন্দোলন ততটা সহিংস হয়নি; এটা অনেকটাই শান্তিপূর্ণই ছিল। এবং এখানে তারা কয়েকটা কৌশল ব্যবহার করেন। তারা বলেন, আমরা প্রতিবাদ হিসেবে যা করতে পারি তা হলো, আমাদের মধ্যে যারা ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন পদবী পেয়েছে, তারা পদবীগুলো বর্জন করতে পারে; ব্রিটিশ সরকারের যে পরিমাণ চাকরি আমরা করি, সেখান থেকে আমরা পদত্যাগ করতে পারি; এবং যেসব মুসলমান আর্মিতে আছে, তারা সরে যেতে পারে। আমরা এইভাবে আন্দোলনগুলো এগিয়ে নিতে পারি।
যখন খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন খেলাফত আন্দোলনও প্রায় অর্থহীন হয়ে যায়। এবং এখানেই সামনে আসে একটা নতুন প্রক্রিয়া—চিত্তরঞ্জন দাস চেষ্টা করেন বেঙ্গল প্যাক্টের মাধ্যমে মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় গড়ে তুলতে। এই ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। সফল হয়েছিলেন মানে, তার প্রস্তাবটা মুসলমানরা খুবই সাদরে গ্রহণ করেছিল। তার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল এরকম যে আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে তিনি আসলে স্বীকার করছেন যে মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র কমিউনিটি, এবং তাদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী থাকা দরকার। একই সাথে তিনি বলছেন, প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি হবে সংখ্যার উপর—যেখানে মুসলমানদের জনসংখ্যা যত, তাদের প্রতিনিধিত্বও তত হবে। ফলে একদিকে যেমন কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশনের বিষয়টি মেনে নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে ডেমোক্রেটিক নীতির ভিত্তি জনসংখ্যাকেও স্বীকার করা হচ্ছে। এই দুটোর সমন্বয়ের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের গণতান্ত্রিক যাত্রায় বেঙ্গল প্যাক্ট এক ধরনের নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়।
প্রস্তাবে বলা হয়, স্থানীয় পরিষদসমূহের প্রতিনিধিত্ব হবে—সংখ্যাগুরু পাবে ৬০% এবং সংখ্যালঘুরা পাবে ৪০%। সরকারি চাকরিতে প্রথমে মুসলমানরা অগ্রাধিকার পাবে, কারণ তাদের রেশিও খুব কম। বর্তমানে এটা ৫৫% হবে এবং যতদিন পর্যন্ত এইটা না হয়, তার আগে ৮০% রাখা হবে। এই প্রস্তাব তৎকালীন কংগ্রেস গ্রহণ করে নাই। খুবই দুঃখজনকভাবে, চিত্তরঞ্জন মারা গেলে এই প্রস্তাবটা কংগ্রেস বাতিল করে দেয়। এই দুইটা ঘটনা- একটা হচ্ছে খেলাফতের পতন, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল। এই দুইটা ঘটনা বাঙালি মুসলমানদের ব্যাপকভাবে মবিলাইজ করছে এই দিকে। আকরাম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী—এদের মতো যারা শেষ পর্যন্ত চাইছিলেন যে কংগ্রেস আমাদের সাথে কো-অপারেট করুক, তারা এরপর থেকেই কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন এবং তারা স্বতন্ত্র মুসলমান সংগঠন তৈরির দিকে হাঁটেন। স্বতন্ত্র মুসলিম পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে এই সময় আমরা কয়েকটা পার্টি দেখি। একটা হচ্ছে বেঙ্গল মুসলিম পার্টি, আরেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি। এই দুইটাই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সালে। এবং দুইটার প্রতিষ্ঠার ভেতরে, নামের ভেতরে আমরা দেখতেছি যে মূলত এরা প্যান-ইন্ডিয়ান না এবং পুরোপুরি প্যান-ইসলামিকও না, এরা মূলত বাঙালি মুসলমানদের স্পেসিফিকভাবে রেকগনাইজ করতেছে এবং তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করতে চাইতেছে।
এখানে বেঙ্গল মুসলিম পার্টির আলোচনা খুবই ইন্টারেস্টিং। বেঙ্গল মুসলিম পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন ব্যারিস্টার আব্দুর রহিম। আলোচনার মধ্যে উনার প্রস্তাব ছিল যে বেঙ্গল মুসলিম পার্টি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আমরা একটা সংবিধান প্রণয়ন করব, আমরা জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা যে সরকার, ওইটা প্রতিষ্ঠা করব, এবং আমাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ হবে। তারা তাদের শেয়ার্ড প্ল্যাটফর্মে এই কথাগুলো বলছে। এবং বাঙালি মুসলমানের এই যে বাঙালি হিসেবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হাঁটা। এইটার ক্ষেত্রে স্যার আব্দুর রহিমের এই বেঙ্গল মুসলিম পার্টি একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হতে পারে।
এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি, বেঙ্গল মুসলিম পার্টি; এখানেই কিন্তু শেষ না। পরে আরেকটা সংগঠন হচ্ছে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি। এই তিনটা সংগঠনের ইশতেহারে আমরা একটা কমন আলাপ দেখতে পাই—তারা ব্রিটিশদের কাছেও নিজেদের নিরাপদ মনে করে না, এবং কংগ্রেসের কাছেও নিরাপদ মনে করে না। এবং এই কারণেই তারা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চায়। তারা বলছে, আমরা আর শুধু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভেতরে থাকব না। আমরা মুসলমানরা এখন থেকে শুধু মুসলমানের বাইরে গিয়ে অন্যান্য ধর্মের মানুষদেরও সাথে রাখতে চাই। অন্যান্য বর্ণের মানুষও এখানে যোগ দিতে পারবে। এ কারণে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি, এই নামটার ভেতরেই একটা বড় মেসেজ আছে। এই নামটা মূলত প্রজাদের, অর্থাৎ রায়তদের নিয়ে। তারা চায় পূর্ববঙ্গে কৃষকদের নিয়ে কাজ করতে। এবং এইখানে পূর্ববঙ্গের কৃষক মানে যে পূর্ববঙ্গের মুসলমান, আমরা জানি কৃষক শ্রেণীর বড় অংশই ছিল মূলত মুসলমান এবং বাকি অংশ অন্তত হিন্দু। তো নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির প্যাটার্নটা মূলত একটা মুসলিম পলিটিক্যাল ফ্রন্ট হলেও তারা এই ফ্রন্টকে সাম্প্রদায়িক রাখে নাই। এখানে সব ধর্মের, সব বর্ণের মানুষকে ইনক্লুড করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, এবং এই নামটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এবং এইটার কারণেই আমরা দেখছি মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস যেখানে প্যান-ইন্ডিয়ান স্ট্যাচার ঘোষণা করতেছে—তারা তাদের পলিসিতে সর্বভারতীয় সমস্যাগুলোর দিকে ফোকাস করছে, মুসলমানদের সমস্যা আলাদা করে ফোকাস করছে, হিন্দুদের সমস্যা আলাদা করে ফোকাস করছে—এই সময়ে এই নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি ফোকাস করতেছে রায়তদের সমস্যা নিয়ে। তারা বলছে, আমরা যদি এই প্রতিনিধিত্ব পাই, তাহলে কৃষকদের সমস্যা থাকবে না, তারপর জমিদারদের ক্ষমতা সংকুচিত করা হবে।
এই যে জমিদারদের ক্ষমতা সংকুচিত করার যে ওয়াদা, এটা ব্যাপকভাবে প্রজাদের মোবিলাইজ করছে, এবং প্রজারা এর ফলে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির জন্য ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি করছে। আর আমরা দেখি, এই কারণেই ১৯৩৭ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির দল, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের দল, কেপিপি (কৃষক প্রজা পার্টি)—তারা নির্বাচনে জয় লাভ করে এবং ক্ষমতায় আসে। তো এইখান দিয়ে আমাদের তৃতীয় পর্বটা শেষ হয় বাঙালি মুসলমানের জার্নিতে। দ্বিতীয় পর্বটা মূলত ছিল বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে একসাথে থাকা–না-থাকার টানাপোড়েন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পোলারাইজেশনের সময়। এই সময় আমরা দেখছি বাঙালি মুসলমান, অবাঙালি মুসলমান এবং বাঙালি হিন্দু—দু’দিক থেকেই কিছুটা সতর্ক হয়েছে। তারা মুসলিম লীগ থেকেও নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে, কংগ্রেস থেকেও নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে। তারা নিজেদের স্বতন্ত্র আইডেন্টিটি তৈরি করার চেষ্টা করছে।
১৯৩৭ সালকে আমরা কেন আবার গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি? ১৯৩৭ সালে প্রথম নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান প্রথমবারের মতো আইনসভায় পা রাখলো—আনুষ্ঠানিকভাবে তারা ডেমোক্রেটিক পদ্ধতির ভেতরে প্রবেশ করল। এই যে আইনসভায় পা রাখা, এই আইনসভায় প্রবেশের মধ্য দিয়ে তাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক্সিস্টেন্স তৈরি হয়। তাদের ব্যর্থতা নিয়ে আমরা অবশ্যই কথা বলতে পারি, অনেক জায়গায় ব্যর্থতা আছে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও কিছু ট্রান্সফরমেশন আছে। সেই ট্রান্সফরমেশনটা হচ্ছে—তারা এই সময়ে পুরো বাংলার প্রতিনিধিত্বের চেষ্টা করছে। এই কারণেই আমরা দেখি, তারা আইনসভায় হিন্দু প্রতিনিধিদেরও আনছে, বাঙালি হিন্দুর সাথে কোলাবোরেশন করছে, এবং শেষ পর্যন্ত অখণ্ড বাংলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সময়টাতে অন্তত তিনটা মন্ত্রিসভা আমরা দেখছি। একটা হচ্ছে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের দুইটা মন্ত্রিসভা। হকের মন্ত্রিসভা প্রথম গঠিত হয় মূলত মুসলিম লীগের সাথে এলায়েন্সের ভিত্তিতে।মানে তারা মন্ত্রিসভায় আসে মুসলিম লীগের সহযোগী হয়ে। কিন্তু এই যে আইনসভা, এই আইনসভাটা পরে ভেঙ্গে যায়। ভেঙ্গে যাওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ আছে। তাদের প্রাথমিকভাবে কয়েকটা বড় সাফল্য ছিল, তারা প্রথমে রায়তদের ক্ষমতায়িত করে, বাঙালি কৃষকদের জন্য জমিদারদের ক্ষমতা কমায়। এই সাফল্যগুলোর জন্য তারা ভালো গ্রহণযোগ্যতাও পায়। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের কিছু ব্যর্থতা ধরা পড়ে—বিশেষ করে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকট। এই অর্থনৈতিক সংকটের কারণে প্রথমে মুসলিম লীগের সাথে তাদের বড় ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়—বিশেষ করে জিন্নাহর সাথে এবং পরে সোহরাওয়ার্দীর সাথে এবং যেহেতু মুসলিম লীগই ছিল তাদের বড় মিত্র, তো মুসলিম লীগ হাল ছেড়ে দিলে মানে মোটামুটি আইনসভা ভেঙ্গে যাওয়া। পরে হক সাহেব দ্বিতীয়বার কোলাবোরেট করেন, তখন গঠিত হয় শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা। শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার শেষ দিকে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায় এবং আমরা দেখি বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়—তাদের ক্ষমতা ছাড়ার কয়েক মাসের মধ্যে। আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষটা দেখা দেয় খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভার সময়, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্রাইসিসটা তার আগের সময় থেকেই তৈরি হচ্ছিল—এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।
এই সময় সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা আমরা আলাদা করে দেখতে পারি, সেটা হচ্ছে পোলারাইজেশন। হক সাহেবের ব্যর্থতাগুলোর সুযোগে মুসলিম লীগ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। আমরা আগেই বলেছি, মুসলিম লীগ আগে থেকে বাংলায় খুব জনপ্রিয় দল ছিল—এমনটা না। বাংলায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, তারপর এক পর্যায়ে মুসলিম লীগ প্রায় ভেঙ্গে পরে, এবং আবার হুট করে পুনর্গঠিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। এই জনপ্রিয়তা তারা পায় প্রথমত মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক দল হিসেবে, এবং পরে মুসলমানদের জন্য পৃথক একটা দেশ দাবি করার মধ্য দিয়ে। বাঙালি মুসলমানের এই ১৯৪৭ পর্যন্ত পার্লামেন্টারিয়ান জার্নি, এই ধারারই এক পর্যায়ে পতন ঘটে। একইসাথে উপনিবেশিক যুগেরও পতন ঘটে, নতুন এক যুগের সূচনা হয়। তো বাঙালি মুসলমানের এই পুরো জার্নিটা আমরা তাত্ত্বিকভাবে যদি ফ্রেম করতে চাই, আমরা দেখব যে বাঙালি মুসলমান প্রথমে কিভাবে একটা পাবলিক স্পেয়ার তৈরি করছে, তারপর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করছে, সংগঠনের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদের দাবি-দাওয়া উত্থাপন করছে, তারপর পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধিদের পাঠাতে চেষ্টা করছে, এবং সর্বশেষ সাংবিধানিক উপায়ে তাদের দাবি-দাওয়া এবং ক্ষমতার চর্চা করার চেষ্টা করছে।
এই পুরো জার্নিটা মোটামুটি বাঙালি মুসলমানের গণতান্ত্রিক, মানে মডার্ন গণতান্ত্রিক স্টেটে তাদের প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে ওঠার জার্নি। এবং আমরা এই জার্নির ক্ষেত্রে দুই–তিনটা সীমাবদ্ধতা দেখতে পাই। প্রথমত হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্যান-ইসলামিজম এবং খেলাফত মুভমেন্ট। এটার সীমাবদ্ধতার কথা আমি এই কারণে বলছি যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের কারণে বারবার বাঙালি মুসলমানের যে জাতীয়তাবাদ এসেছে, সেটা ঠিক প্রথমে বাঙালি মুসলমানের নামে আসেনি—এটা এসেছে প্যান-ইসলামিস্ট পরিচয় নিয়ে। এই কারণে বাঙালি মুসলমানের অগ্রগতির যে ধারা, যেটাকে আমরা এখন “বাঙালি মুসলমান” বলে কয়েন করছি, তার জন্য একটা বড় সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিকল্প হিসেবেই খেলাফতের আইডিয়া উঠে এসেছে। বাঙালি মুসলমান অনেকটা এভাবে ইমাজিন করেছে যে, বাঙালি হিন্দুরা যেমন তাদের ‘ইন্ডিয়া’ নিয়ে ফিক্সড, বাঙালি মুসলমান বা মুসলমানদের জন্য তো সারা বিশ্ব আছে—উম্মাহ আছে। ঠিক এই কারণেই তারা ভাষা প্রশ্নে কিছুটা টানাপোড়েনে পড়ে—আমরা কি বাংলায় যাব, নাকি উর্দুতে যাব, নাকি আরবিতে যাব? এই ধরনের নানান দ্বন্ধের ভেতরে বাঙালি মুসলমান দীর্ঘদিন আটকে ছিল, যেগুলোর অনেকগুলোরই মীমাংসা হয়নি অনেকদিন পর্যন্ত।
তারপরও আমরা বলতে পারি, খেলাফত আন্দোলনের একটা উপকারিতা ছিল। খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মূলত আমাদের পদ্ধতিগত আন্দোলনের প্রবণতা তৈরি হয়। এর আগে আমাদের সব ধরনের বিদ্রোহ ছিল অনেকটা বাইরে থেকে, বিচ্ছিন্নভাবে, দূরবর্তী ফ্রন্টে। কিন্তু এখানে এসে আমরা প্রথম সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে, শান্তিপূর্ণ ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে লড়াই করার একটা প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করি। তো এই সময়ে এই আলোচনা কেন এত প্রাসঙ্গিক, সেটা ভাবার বিষয়। কারণ বাঙালি মুসলমান বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে সবসময় এই সমীকরণের মধ্যে থাকে—বৃহত্তর মুসলিম দুনিয়ার ভেতরে তাদের স্টেক কতদূর, আর নিজেদের নেটিভ জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের স্টেক কতদূর। এই সমীকরণের মধ্য দিয়েই তারা যখন স্বতন্ত্র একটা বর্গ হিসেবে “বাঙালি মুসলমান” পরিচয় নির্মাণ করতে যায়, তখন তাদের অনেক কিছুর সাথে ডিল করতে হয়েছে, অনেক কিছুর সাথে তারা পেরে ওঠেনি, এবং অনেক কিছুকে তাদের বিলম্বে গ্রহণ করতে হয়েছে।
যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করছে—যেগুলা ছোট ছোট বিদ্রোহ, ব্রিটিশবিরোধী হলেও সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে—ততক্ষণ পর্যন্ত তার ফল খুব বেশি সুবিধাজনক হয়নি। ১৮শ শতক এবং ১৯শ শতকের প্রথম দিকের আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের কাছে মুসলমানরা আরও বেশি “পার্মানেন্ট এনিমি” টাইপ ইমেজ পেয়েছে, হান্টার এ কথাই বলছেন যে মুসলমানরা এক ধরনের স্থায়ী শত্রুর মত। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যখন দেখি, মুসলমানরা যখন তাদের প্রতিনিধিত্বশীল, পদ্ধতিগত এবং গণতান্ত্রিক ধারায় নিজেদের হাজির করতে শুরু করেছে, তখন তারা নিজেদের ক্ষমতায়িত করতে পেরেছে, নতুন পরিবেশে নিজেদের অধিকার আদায় করতে পেরেছে, এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের পথে বড় ধরণের সমস্যা হয়নি। তো আমার মনে হয়, বর্তমান সময়ে যখন বারবার খেলাফত বিতর্ক, বাঙালি মুসলমানের পরিচয় নির্মাণের বিতর্ক, বাঙালি মুসলমানের নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়—তখন এই ধরনের ঐতিহাসিক আলাপ নতুন করে প্রাসঙ্গিকতা পায়। কারণ আমরা এখান থেকে দেখতে পারি, আমাদের বাঙালি মুসলমানের যে প্রিভিয়াস জার্নি, তার সঙ্গে আমরা কতটা কানেক্টেড, এবং এর ফিউচার কী রকম হতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে।