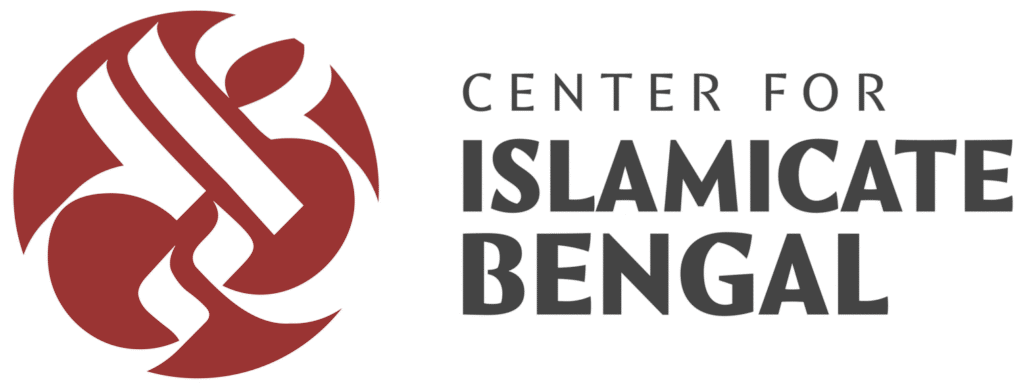মধ্যযুগের সাহিত্যে কসমোপলিটান ধারা বুঝার ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং সাহিত্য আমার কাছে বড় উপাদান। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে করি যে, কেবল মধ্যযুগ নয়; শুরু থেকে-ই বাংলা সাহিত্য কসমোপলিটান চিন্তা নিয়েই জন্মই হয়েছে। কারন, আসলে প্রাচীন বাংলায় একেবারে ধরার মত বড় কোন বাংলা সাহিত্য খুঁজে পাই না। বাংলা সাহিত্যের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা প্রধানত মধ্যযুগের সুলতানী পর্বে। ফলে সেই সময় থেকেই আমরা কসমোপলিটান ধারা পাচ্ছি—লোকজ সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য যার পরবর্তী বিকাশকে দোভাষী সাহিত্য বলা হচ্ছে, ধর্ম আশ্রিত সাহিত্য এবং ধর্ম থেকে সরে আসা সাহিত্য। ফলে শুরু থেকেই নানা কিছুর মধ্য দিয়ে এরকম একটি কসমোপলিটান ধারা রচিত হয়েছে।
প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলার বাস্তবতা ছিল ধর্মভিত্তিক। ধর্ম বহির্ভূত সমাজ কাঠামো তখনও তৈরি হয়নি। ফলে আমি যখন প্রত্নতত্ত্বের জায়গা থেকে দেখি, বিশাল পাল সাম্রাজ্যের বিখ্যাত পাল রাজাদের কথা শুনি, তখন মাঝে মাঝে ভাবি— তারা কি গাছতলায় রাত্রি যাপন করতেন? কারণ আমরা দেখছি যে, পালযুগের স্থাপত্য ছিল বিহার এবং স্তুপা স্থাপত্য অর্থাৎ ধর্মকেন্দ্রিক। তাহলে বিখ্যাত ধর্মপাল থাকতেন কোথায়? নিশ্চয় থেকেছেন কোথাও! তখন বুঝতে হবে যে, সেকালে প্রাসাদ নির্মাণের উপকরণসামগ্রী সীমিত ছিল। চাইলে-ই রাজপ্রাসাদ, প্রশাসনিক ভবন এবং ধর্মীয় উপসানালয় আলাদাভাবে বানানোর সুযোগ ছিল না। যেহেতু সমাজ ছিল ধর্মাশ্রিত ছিল, তাই তারা যতটুকু চুন, সুরকি এবং ইট পুড়াতে পেরেছেন তা দিয়ে ধর্মীয় ইমারত বানানোকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনও হতে পারে যে, বানানোর আগে নির্মান সামগ্রী ফুরিয়ে গেছে; সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। ফলে রাজপ্রাসাদ কিভাবে বানাবে? তবে তারা বানিয়েছিল। হয়তো সেগুলো স্থানীয় রীতিতে করা হয়েছিল—কাঠের বাড়ি বা মাটির বাড়ি। যেগুলো এত শত বছর পরে আমরা খুঁজে পাবো না। তাহলে ধর্ম এবং ধর্মের আশ্রয়টাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারছি না। মধ্যযুগেও এমন ছিল। সুলতানি যুগে বাংলা জুড়ে-ই ধর্মীয় স্থাপত্য, বিশেষভাবে মসজিদ লক্ষ্য করা যায়। খুব সামান্য সমাধি স্থাপত্য ও মাদ্রাসা পাওয়া যায়। মোঘল আমলে বৈচিত্র্য চলে আসে সেটা আলাদা বিষয়। ষাট গম্বুজের পেছনে অর্ধ খননকৃত খান জাহানের প্রাসাদ পাচ্ছি। তাছাড়া সবই তো ধর্মীয় স্থাপত্য। এটা ছিল সেই সময়ের বাস্তবতা।
ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ধর্ম এবং সেটা যদি ভারতবর্ষীয় হয় তাইলে ছন্দটা একরকম। এটাকে আমি প্রাচীন যুগ বললাম। তারপরে যেদিন ছন্দ পরিবর্তন হয়ে গেল অর্থাৎ শাসক আসল বাইরে থেকে—তার ধর্ম হল অন্যরকম এবং রক্ষণশীল হয়ে গেল কিংবা সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ঘটানোর মাধ্যমে একধরনের রূপান্তর হল। এ রূপান্তরটাকে আমি মধ্যযুগ বললাম। তারপরে সময়ের পরিক্রমায় আবার একটি বড় দাগের রূপান্তর দেখা গেল। সেটাকে বললাম উপনিবেশিক যুগ; আধুনিক বললাম না। কারণ কাঠামোটি ছিল উপনিবেশিক ধারা। অর্থাৎ যে পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসে শাসকরা হলেন সর্বভারতীয় এবং ভারতবর্ষে দুটো বড় ধর্ম—বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম—অরিজিনেট করেছে সে পর্যন্ত ছন্দ একরকম ছিল। সে সময়টা ত্রয়োদশ শতকের একদম শেষ পর্যন্ত ছিল অর্থাৎ, বখতিয়ার খিলজীর আসার আগ পর্যন্ত।
সুফিজম নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে মনে পড়লো আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহিন চৌধুরী স্যারের কথা। এখন তিনি ইহজগতে নেই। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে স্যারের লেখা ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তিন খন্ডের বাংলার ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল। মধ্যযুগ পর্বের ইতিহাস লেখার কাজে আমি স্যারের সাথে খানিকটা সম্পৃক্ত ছিলাম। তো তখন আমি স্যারকে বললাম যে, স্যার, আপনার সাথে আমার একটি ছোট্ট দ্বিমত আছে। এ কাজটা অনেকে-ই করে; আপনিও করছেন। তা হচ্ছে সুফিদের তৎপরতা উত্তর ভারতে যে ধারায় চলেছে বাংলায় কিন্তু একেবারে-ই সেটা চলেনি; সেটা ঘুরে-ফিরে একেবারেই বঙ্গজ হয়ে গেছে। আমি স্যারকে বলেছিলাম যে, বাংলার বৈঞ্চব ও বাংলার সুফিজম নিয়ে এন্ট্রি লেখতে হলে এখানকার বিশেষজ্ঞ লাগবে।
তো এই সময়ে এসে আমরা রিচার্ড ইটনের বইয়ের কথা বলি। খুবই চমৎকার যুগান্তকারী একটি কাজ। তবে আমি উনার কাজের সমালোচকও বটে। আমার মধ্যযুগের বাংলার মুদ্রা ও শিলালিপির যে বইটি আছে সেটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হওয়ার সময় তিনি আমার কাছে এসেছিল এবং আমি তাকে দেখিয়েছিলাম যে, কয়েকটি জায়গায় তাঁর ধারণা গ্রহণ করার মতো না । তিনি বাংলায় ইসলামাইজেশনের যে থিওরি দিয়েছেন তার সাথে আমার শিক্ষক আকবর আলী খান স্যারও সব জায়গায় একমত হতে পারেননি—পারার কথাও না। উত্তর-ভারতের ইসলামাইজেশনের ছাপটা ইটনের কাজে এসে পড়েছে। তিনি এখানে থেকে তাঁর গবেষণার কাজটা করেছেন। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে তার বইয়ের বিশাল রেফারেন্সে এনামুল হকের ‘A History of Sufism in Bengal’ বইয়ের নাম নেই। এখন পর্যন্ত আমরা মনে করি যে, এটা সাংঘাতিক গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা বই। উনার এই কাজের বাহিরে নতুন নতুন সোর্স কিছু আসলে আসতে পারে। কিন্তু সেই কাঠামোটা অতিক্রম করা এখন পর্যন্ত সহজ নয় বলে আমার মনে হয়েছে। অথচ এই বইটি বাদ দিয়ে ইটন বাংলার সুফিজম নিয়ে আলোচনা করে ফেলছেন। ফলে তাঁর আলোচনায় সর্বভারতীয় সুফিজমের ছাপ পড়েছে। ফলে আমরা যখন বাংলার সুফিজম আলোচনা করব সেখানে সুফিজমের তাত্ত্বিক ছাঁচ কখনোই প্রতিফলিত হবে না।
তো শুরুতে এজন্য বলেছিলাম যে, বাংলা সাহিত্যের জন্মই হয়েছে একটি কসমপলিটান চিন্তা থেকে। কারন, বাংলা সাহিত্যের বিকাশ প্রধানত সুলতানী যুগে হয়েছে। সুলতানরা বহিরাগত মানুষ ছিলেন। তারপরেও তারা এদেশের সাহিত্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে গেছেন। ফলে একটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবেই চলে এসেছে। ‘নবী বংশ’ বা মুসলিম প্রণয়-উপাখ্যানগুলো একটু পরে এসেছে। ১৩ শতক থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে অন্তত আমাদের ধারণ করতে হবে। মুসলিম কবিরা এবং লেখকরা আত্মপ্রকাশ করেছেন একটু পরের দিকে। কিন্তু আগে থেকে বাংলা সাহিত্য রচিত হয়ে আসছে এবং তার শুরুটা আমরা মঙ্গল কাব্যের যুগ থেকে ধরতে পারি।
মঙ্গল কাব্যগুলো নানা রকম দেব-দেবীর মঙ্গল বা মঙ্গলিক চিন্তা ধারণ করে। কিন্তু আমাদের এখানে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়েছে মনসামঙ্গল ধারাটি। এই কাব্যগুলোর মধ্যে সেই সময়ের কবিরা ইতিহাস ও সময়ের বাস্তবতা ধারণ করেছেন। যেমন রাজা গণেশ তিনি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এবং ইলিয়াসশাহী বংশের তৃতীয় শাসক। তিনি মারা যাওয়ার পর একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং তার সূত্র ধরে অল্প সময়ের জন্য হলেও হিন্দু নেতার উত্থান ঘটে অর্থাৎ বাংলার মুসলিম শাসনের একটি ছোট্ট অবসান বা বিরতি ঘটে বলা যায়। এই দেড়-বছর বা পৌনে-দুই বছরের বিরতির মধ্যে কারা শাসক হয়েছেন সে ব্যাপারে প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র আমাদের সাহায্য করতে পারছে না। তারপরেও দু-একটা মুদ্রা পাওয়া যায়। একটি মুদ্রা জারি করেছেন দনুজমৰ্দ্দন দেব, আরেকটি করেছেন মহেন্দ্রদেব।
বাংলা সাহিত্যে এই নামগুলো আছে; গণেশের নাম নেই। উল্টোদিকে দনুজমৰ্দ্দন দেবের নাম ইতিহাসে নেই— না প্রাচীন যুগে; না মধ্য যুগে। ফলে নানাভাবে গবেষণা করতে করতে দেখা গেল যে, এই দনুজমৰ্দ্দন দেব আর অন্য কেউ নন। তিনি হচ্ছেন রাজা গণেশ। তাহলে নিজের নামের পরিবর্তে অন্য নাম কেন নিলেন? কারন, দনুজমর্দন দেবের দনুজ মানে হচ্ছে দানব। তার চোখে মুসলিম শক্তি হচ্ছে দানব যারা এ দেশ দখল করেছে। সেই দানবকে মর্দন করে, মথিত করে যে দেবতা দাঁড়ালেন গণেশ হচ্ছে সেই দেবতা।
তাহলে এর ভেতর থেকে বাকি কথাগুলো বেরিয়ে আসে। কারণ মুসলমান শাসকদের রাজ-ভাষা ফারসি কিন্তু তারা মুদ্রায়-শিলালিপিতে আরবি ব্যবহার করছেন ধর্মীয় ধারণা থেকে। সেই ধারণাগুলোর মধ্য দিয়ে তারা এক ধরনের বিশেষ রীতি তৈরি করে ফেলেছেন। তা একেবারে উল্টে দিলেন দনুজমৰ্দ্দন দেব। মুসলমানরা রপ্য মুদ্রা ব্যবহার করতেন, তিনি তাম্র্য মুদ্রা ব্যবহার করলেন। মুসলমানরা কলেমা ব্যবহার করছেন, তিনি সেখানে লিখলেন ‘দনুজমৰ্দ্দন দেবস্য, চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য”। মানে চণ্ডীর কাছে তিনি নতজানু হচ্ছেন।
চণ্ডীতো দুর্গারই লোকজ সংস্করণ। চন্ডীমঙ্গল কেন হচ্ছে? বা কখন চণ্ডী আসে? কারণ চণ্ডীর তখনই দরকার পড়ে যখন একটি অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ধর্ম নিমজ্জিত হয়। তখন আর মহামায়া দুর্গা দিয়ে কাজ হয় না। তখন দরকার হয় চণ্ডরূপধারিণী চণ্ডীকে। সেজন্য তিনি তার মুদ্রায় লিখেছেন ‘চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য’। কারণ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং মুসলিম শক্তির অবসান ঘটিয়েছেন। কিন্তু তার তো কোন শক্তি নেই যেহেতু সুলতানদের সামরিক বাহিনীর অধিকাংশই সুলতানদের অনুগত ছিল। তার এই শক্তির সংকটের সময় আমরা দেখেছি যে, সুফিরা জৈনপুরের সুলতানকে আহবান জানালেন মুসলিম শাসন বিপন্ন বলে। তার আসার পেয়েই গণেশ পাল্টে গেলেন এবং তার ছেলেকে মুসলমান বানিয়ে দিয়ে গেলেন। শক্তি সংকটের কারণে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন দেবীর কাছে যেন তার চণ্ডরূপ দিয়ে তিনি হিন্দু শাসনের পুনঃস্থাপন করেন।
আবার মনসামঙ্গলের মনসা হচ্ছেন লোকজ দেবী। সেই লোকজ দেবীকে ধারণ করে বিজয়গুপ্ত পদ্মপুরাণ লিখেছেন। সেখানে তিনি শুধু মনসা দেবীকে নিয়ে লিখেছেন না। পাশাপাশি তার নিজের চারপাশের জগৎ তার লেখার সামনে চলে আসছে। তিনি বরিশালের ফুলশ্রী গ্রামের মানুষ। তিনি তার মনসামঙ্গলের মূল থিম থেকে বেরিয়ে এসেও তিনি তার ফুলশ্রী গ্রামের পাঠশালার কথা বলে ফেলছেন। উনি যে পাঠশালার বিশদ বিবরণ দিচ্ছেন তাতে বুঝা যায় কবিরা জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বৈশ্বিক বলতে আমাকে যে বিশ্বজুড়ে ছুটতে হবে ব্যাপারটা তেমন নয়। মূলত হচ্ছে চিন্তাটা।
শাহ মুহম্মদ সগীরের ‘ইউসুফ-জোলেখা’ বা দৌলত উজির বাহরাম খানের ‘লায়লী-মজনু’ কাব্য ফার্সি থেকে অনূদিত। আরবি উপন্যাসের অনেক ধারা চলে পারস্যে। সেগুলো আবার ফারসি ধারায় লেখা হয়। এবং ফার্সি ভাষী সেসব কবিরা বাংলায় চলে আসে। বাংলার কবিরা আবার সেটা গ্রহণ করেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে একটি মিশ্র ধারা তৈরি হয়েছে এবং একটি বিশ্বজনীন একটি চিন্তার স্ফুরণ ঘটেছে। এভাবে দৌলত উজির বাহরাম খান তার কাব্যে অপূর্বভাবে ফারসি কাঠামোটাকে ভেঙে ফেলেন। তিনি লায়লী-মজনু কাব্যে একটি পাঠশালার ছবি বর্ণনা করেছেন এভাবে—
সুন্দর বালকগণ অতি সূচরিত।
একস্থানে সভানে পড়এ আনন্দিত।।
সেই পাঠশালায় পড়এ কথ বালা।
সুচরিতা সুললিতা নির্মলা উজ্জ্বলা।।
—পাঠশালায় লায়লী
সেখানে তিনি সহশিক্ষার কথা বলে ফেলেছেন। আমি একবার একজন বিদগ্ধ নারীবাদী গবেষককে আলোচনা করতে শুনলাম। তিনি মধ্যযুগকে খুবই নারীদের অবরুদ্ধ করার একটি সময় মনে করছেন। আমি বিনয়ের সাথে বললাম যে, বর্তমানের সাথে তুলনা করলে আগে আরো ভালো ছিল। যেমন বর্তমানে আমরা যে সহশিক্ষার কথা বলছি সেটা সুলতানি আমলে ছিল যেমনটা আমরা কবিতায় দেখতে পাচ্ছি। এই চিন্তার উদার নৈতিকতাকে আমরা যখন আবদ্ধ হয়ে আলোচনা করব তখন কিন্তু ইতিহাস এবং সাহিত্য খন্ডিত হবে।
বখতিয়ার খিলজি আসার মধ্য দিয়ে ইসলামীকরণের একটি ব্যাপার ঘটেছে—ইতিহাস কিন্তু তা বলবে না এবং মানবেও না। কারন, বখতিয়ার খিলজী দিল্লির সুলতানের আদেশ পালন করতে এখানে এসেছিলেন। ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা আর ইসলামীকরণের মধ্যে একটি তফাত আছে। কোন কোন সুলতান ছিলেন যারা ইসলাম প্রচারের জন্য তেমন কোন ভূমিকা রাখেননি। হয়তো সহযোগিতা করে থাকতে পারেন।
এদেশে ইসলামাইজেশন একমাত্র সুফি-সাধকরা করেছেন। তারা সফল হয়েছেন। তারা দুইভাবে এসেছেন। যখন কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন যুগের শাসন চলছে এবং একই ধর্মের শূদ্র শ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না তখন বাংলায় সুফিদের আসা শুরু হয়েছে। একটি বড় রকমের প্রতিরোধের মুখে তাদের যাত্রা শুরু করতে হয়েছে এবং তারা সফল হয়েছে এই জন্য যে বাংলায় যে সুফিরা আসছেন তাদের জনপ্রিয় ধারা ছিল যথাক্রমে চিশতিয়া, কাদেরিয়া এবং নকশবন্দিয়া তরিকা। সোহরওয়ার্দিয়া ধারার আগে যত সুফিরা এসছেন তাদের প্রধান ফিলোসফি ছিল Love For The God, Love For The Humanity অর্থাৎ ইসলামীকরণের চিন্তা তখনও আসেনি। এইটার তফাতটা না করতে পারলে আমাদের মূল্যায়নটা ঠিক হবে না। আমাদের সেই মূল্যায়নটা করতে হবে যে তারা এটা কেন করেছেন। কারণ তখন সাংঘাতিকভাবে নিপীড়িত ছিল শূদ্ররা। বাংলার ইতিহাস যদি আমরা কঠিনভাবে পর্যালোচনা করি সেই খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই আর্যদের বাংলায় ঢুকতে অনেক সময় লেগেছে। কারণ এদেশের মানুষের স্বভাব হচ্ছে প্রতিবাদ করা। তারা অনেকদিন পর্যন্ত আটকে রেখেছিল আর্যদের এ দেশে আসা। কিন্তু যখন মৌর্য শাসন শুরু হলো এবং অশোক উত্তর-বাংলা দখল করলেন—সেই সুযোগে আর্যরা এখানে ঢুকে পড়ে। তাহলে এই যে একটি সমাজ বাস্তবতা তার ভেতর থেকে কবি এবং সাহিত্যিকরা বেরিয়ে আসতে শুরু করলেন। তারা তো এই সমাজ বাস্তবতাকে এড়াতে পারবেন না। তার একটি প্রতিফলন তাদের মধ্যে ঢুকবেই।
জাত ও সিফাত সুফি ফিলোসফির প্রধান কথা। সুফিরা সাংঘাতিকভাবে জাগতিক ছিলেন। তাদের ফিলোসফি অনেকটা আমার কাছে বিগ-ব্যাং-থিওরির মতো। এটা আল কোরআন থেকেই বলা; বিচ্ছিন্ন কিছু না। সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর অনু-পরমাণু। এরকমভাবে সবকিছু তার সেফাত দিয়ে তৈরি। ফলে সুফিরা মনে করেন মানুষ খোদার-ই অংশ। আমরা যে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে গেলাম তাহলে এখন আমাদের কর্তব্য কী? আমাদের একটি-ই কর্তব্য তা হচ্ছে কেন্দ্রে ফিরে যাওয়া। তো এই কেন্দ্রে ফিরতে হলে আমাকে সাধনা করতে হবে। সুফি হচ্ছেন তিনি যিনি চার ধরনের সাধনা ধারাবাহিকভাবে করে সফল হয়।
আমরা সুফি সাহিত্যে এর চমৎকার প্রতিফলন দেখি। সেখানে চারটা ফানার কথা বলা আছে। ফানা মানে একাকার হয়ে যাওয়া। ফানা ফি-শেখ, শায়খ থেকে এসছে। তার মানে যথার্থ পীরের কাছে যেতে হবে, তার মুরিদ হতে হবে। সব পীরেরাই ধর্মীয় রিচুয়ালের বাহিরে নিজেরা কিছু প্র্যাকটিস দিয়েছেন মুরিদরেরকে আমল করার জন্য। সেগুলো যে খুব সোজা এমন নয়। সব মুরিদ যে তা পুরোপুরি মানতে পারেন তাও না; কিন্তু সুফি হতে হলে সেটা অনুসরণ করতে হয়। তিনি যদি এ স্তরে সফল হন তাহলে তিনি দ্বিতীয় স্তরে—ফানা ফি-রাসুল—যাবেন। হাদীসে রাসুল যা বলেছেন তার প্রত্যেকটা যিনি সফলভাবে আমল করতে পারবেন তিনি ফানার দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করবেন। তারপর ফানাফিল্লাহ—আল্লাহ আল কোরআনে যা যা নির্দেশ দিয়েছেন এই নির্দেশগুলো পূর্ণ করলে তখন তিনি ফানাফিল্লাতে চলে যাবেন। এখানে তিনি স্রষ্টার সাথে একাকার হয়ে যাবেন। সর্বশেষ বাকা বিল্লাহ। যিনি অধিক প্রতিভাবান তিনি পরকালে এই সম্মান পাবেন। এই যে চর্চার মধ্য দিয়ে সুফিরা চলছেন তাদের কিন্তু ইহকালের চাওয়া-পাওয়া থাকে না এবং তারা তারা যদি বলে ফেলেন বেহেশত-দোযখ দিয়ে আমি কী করব! আর এটা শুনলে কারো তেরে আসা ঠিক হবে না। কারণ তিনি তো অনুভব করছেন যে, তিনি একাকার হয়ে গেছেন। এই ব্যাপারটা কি বাগদাদে আমরা দেখিনি? আনাল হক হাসছে আর বলছে, I’m The God,I’m The God। কত বড় শিরক! তাকে মেরে ক্ষত-বিক্ষত করে বাদশা হারুনুর রশিদের দরবারে নিয়ে আসা হল, তবুও সে হাসে! কারন তিনি মনে করলেন যে, আমি সেই শক্তির সাথে একাকার হয়ে গেছি।
আমরা একই জিনিস বৈষ্ণব সাহিত্যগুলোতেও দেখতে পাই। যেমন চৈতন্য চরিতামৃতে বলা আছে যে, বৈঞ্চবকে নির্যাতন করা হচ্ছে। সে বলছে আর হাসছে—মুই সেই, মুই সেই। মানে আমিই সেই, অর্থাৎ I’m the god। তাহলে ‘আনাল হক’- এর সাথে ‘মুই সেই’য়ের তফাত কোথায়? কোন তফাত নেই। সুফি চিন্তার জাত-সিফাতের মত চৈতন্যধারায় রাধাকৃষ্ণ অনেকটা তেমন। চৈতন্য-উত্তর যুগে রাধাকৃষ্ণ বিশেষভাবে দাঁড়িয়ে গেল। এখানে রাধাকৃষ্ণ রূপক। রাধা মানে জাত অর্থাৎ মানব জীবন। কৃষ্ণ হচ্ছে খোদার প্রতীক। কোন তফাত নেই আসলে। এই যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এইজন্য কলোনিয়াল পিরিয়ড আসার আগ পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দের ইতিহাস নেই। সে অবকাশও ছিল না।
চৈতন্যের জন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে থেকে সুফিরা এখানে এসেছে। সুফিদের প্রভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু জনগোষ্ঠী প্রান্তিক জায়গায় চলে আসছিল। এর মধ্যে ব্রাহ্মণরা যে নীতি গ্রহণ করেছিল সেটা বুমেরাং হয়ে গিয়েছিল। তারা শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মান্তর থামাতে চেয়েছে। বরং মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মুসলমান-ই হচ্ছিল। দলে-দলে আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হচ্ছে—সেটা ইতিহাস বলবে না। ইতিহাস দেখবে যে, জীবন-জীবিকার বাস্তবতায় তার এখন মুসলমান হওয়া-ই শ্রেয়। এ পরিবর্তনের মুখ থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে ৫০০ বছর ধরে কেউ রক্ষা করতে পারছিল না। চৈতন্যর যদি জন্ম না হতো আমি খুব আতঙ্কিত বোধ করি যে, হিন্দু-বৌদ্ধদের আর পেতাম কিনা! চৈতন্য বোধ করলেন যে, এইভাবে হবে না। চৈতন্যের এ আন্দোলনকে আমরা অনেক-ই বৈষ্ণববাদ বলি। এর উপর রমাকান্ত চক্রবর্তীর ‘Vaishnavism in Bengal’ নামে একটা বিখ্যাত বই আছে। ১৪-১৫ বছর আগে শান্তিনিকেতনে একটি সেমিনারে আলোচক হিসাবে গিয়েছিলাম। সেখানে বললাম যে, “উনার বই দ্বারা অনেক ঋদ্ধ হয়েছি। উনি বেঁচে থাকলে আজকে বলতাম যে, দয়া করে কি আপনার বইয়ের শিরোনাম পরিবর্তন করবেন!” এ কথা শুনে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে! রমাকান্তের বইয়ের নাম পরিবর্তন করতে বলছি! ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে বলছি—চৈতন্য যেটা করেছেন সেটা মোটেও বৈষ্ণববাদ নয়। ‘ইজম’ বা মতবাদ তো একটি নতুন ধারণা; চৈতন্য তা করেননি। এখন এই কথাটার তাৎপর্য না বুঝলে তো বৈষ্ণব সাহিত্য বুঝবো না, মুশকিলটা তো এখানে।
আমরা যে সাহিত্যের কসমোপলিটান ধারা খুঁজতে চাচ্ছি এটা তো খুব জরুরি। কারন, চৈতন্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন হিন্দু সমাজকে। তিনি বুঝছেন যে, ব্রাহ্মণরা যেভাবে রক্ষা করতে চেয়েছে সেভাবে হবে না। কারন, সুফিদেরকে সাধারণ মানুষ ভালোবেসে ফেলেছে। হিন্দুদেরকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিতে হলে ওইরকম ভালোবাসার জায়গা তৈরি করতে হবে। এটাকেই বলে সোশ্যাল রিফরমেশন। তিনি সমাজকে সংস্কার করতে চেয়েছেন এবং সংস্কার করতে চেয়ে তিনি যে ধারাটা তৈরি করলেন তার মধ্যে ধর্ম সংস্কার নয়; সমাজ সংস্কারটাই বড় হয়ে দাঁড়ালো।
যখন হিন্দুরা দেখল যে সুফিদের কাছে গিয়ে ভালো লাগার মতো বেশ কিছু জিনিস আছে। তন্মধ্যে একটা হল হালকা যেটাকে জিকির বলে। এই হালকাগুলো তালের সাথে সমস্বরে জিকির করছে ঈশ্বরের। এটা একটা ভালো লাগার বিষয়। চৈতন্য ভাবলেন, আমিও ওই রকম করব। তিনি আলাদা বৈষ্ণব মন্দির বানালেন। মন্দিরে শূদ্রের ঢোকা নিষেধ ছিল। এবার তিনি সবার জন্য দরজা খুলে দিলেন। তিনি হালকার আদলে কীর্তন চালু করলেন—
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে”
তো হিন্দুরা যখন এই রকম আয়োজন পেয়ে গেল তাহলে কেন তারা আর সুফিদের কাছে যাবে? আরেকটি বড় আকর্ষনীয় জিনিস ছিল সামা গান যা ইরান থেকে সুফিরা নিয়ে এসেছিলেন। মাইজ-ভান্ডারি গান কিন্তু সামা গানের-ই একটি অপভ্রংশ, ঢোল-করতাল এগুলো বাজিয়ে নেচে-নেচে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত সংগীত। সেটা খুবই একটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। চৈতন্য ভাবলেন, আমিও এমনটা করব। এবার তিনি কীর্তনের সাথে জুড়ে দিলেন সংকীর্তন। অর্থাৎ এখানেও ঢোল-করতাল মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিয়ে হরে-কৃষ্ণ হরে-রাম ঘুরে-ঘুরে ও নেচে-নেচে করছে। আরেকটু এগিয়ে গেলেন চৈতন্য। এবার করলেন নগর সংকীর্তন। গলায় ঢোল ঝুলিয়ে মিছিল করে নবদ্বীপের নগরে নগরে নগরে ঘুরে ঘুরে হরেকৃষ্ণ গাইতে লাগলেন। এভাবে হিন্দু সমাজ নতুন একটি অবয়ব পেয়েছে চৈতন্যের মধ্য দিয়ে।
এই অবস্থা দেখে প্রমাদ গুণতে লাগল বর্ণ হিন্দুরা। কারণ তারা তো এতদিন শূদ্রদের বুঝিয়েছে যে, এটা-সেটা করা যাবে না—করলে মহাপাপ হবে। এখন চৈতন্য নিজেই ব্রাহ্মণ হয়ে তাদের নিয়ে মিছিল করছেন। এমনিতে-ই তাদের রাজক্ষমতা মুসলমানরা অনেক আগে কেঁড়ে নিয়েছে। সমাজের অধিপতি হিসাবে যতটুকু অবস্থা ছিল সেটাও চৈতন্যের সংস্কার আন্দোলনের ফলে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তারা আর মানতে পারলেন না। এবার তারা নবদ্বীপের মুসলমান কাজীর কাছে নালিশ দিলেন। বিচারক সমন পাঠালেন। চৈতন্য তখন বিপ্লবী পুরুষ। তিনি নবদ্বীপে ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ বলে নগর-সংকীর্তন করছেন। তার কাছে পেয়াদা গেল। তারপর দেখা গেল যে, সবাই দলবল নিয়ে কাজির বাড়ি ঘেরাও করেছে। কাজী তো সুলতানের পরের স্থানীয় প্রতিনিধি। বিশাল লাঠিয়াল বাহিনী আছে তাঁর। তিনি চাইলে-ই মেরে বের করে দিতে পারতেন। তিনি তা করেন নি; তিনি থামাতে চাইলেন। তিনি চৈতন্যকে জড়িয়ে ধরে বললেন যে, গ্রাম-সম্বন্ধী চক্রবর্তী হয় মোর চাচা, দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাচা। অর্থাৎ, তোমার নানা নিলাম্বর চক্রবর্তী; সেই সম্পর্কে তুমি হও আমার ভাগিনা। যখন ধরিয়ে ধরে এ কথা বললেন তখন তাঁর রাগ চলে গেল। তারপর চৈতন্য বললেন, আমাকে কেন ডেকেছেন? কী অপরাধ? কাজী বললেন, এই যে দেখো তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। সেখানে পৌরাণিক শব্দ ইত্যাদি ব্যবহার করে তারা চৈতন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল—
“হিন্দু ধর্ম নষ্ট হইল পাষণ্ডী সঞ্চারী
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বারবার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজার
হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি।
সর্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য হয় হানি॥”
চৈতন্য তখন কাজী সাহেবকে বললেন, আপনি বলুন তো আমি কি অন্যায় করেছি? আমার ধর্মের সবাইকে নিয়ে আমি কৃষ্ণনাম করছি। একজন মুসলিম কাজীর কাছে সেটা তো অন্যায় কিছু হবে না। কারন ইসলামে তো সেই ধারাটা নেই। কাজী বললেন যে মিথ্যা মামলা এবং তিনি সেটা খারিজ করে দিলেন।
বৈষ্ণব সাহিত্যগুলো তখনই যে তৈরি হয়েছে তা নয়। মানুষ বৈষ্ণব ভাব বন্যায় এতটা ডুবে গিয়েছিল যে চৈতন্য মারা যাওয়ার পর চৈতন্যকে নিয়ে তাঁর পরিকর বা শিষ্যরা জীবনী লিখে ফেললেন। এটাই হল বাংলা সাহিত্যে প্রথম নতুন ধারা—জীবনী সাহিত্য। চৈতন্য না থাকলে এ ধারাটা তৈরি হতো না। হয়তো হতো আরো পরে অন্যভাবে।
আমি এ আলোচনাটা করলাম ‘নবী বংশ’ অথবা ‘রসুল বিজয়’ কাব্যের কাছে পৌঁছার জন্য। আমরা চৈতন্য সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরিছি সবই তার জীবনী সাহিত্য থেকে। বিশেষভাবে দুইটি—একটি হচ্ছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’; আরেকটি হচ্ছে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ‘চৈতন্যভাগবত’। সেখানে প্রচন্ডভাবে এই ব্যাপারগুলো আছে। আরো আগে যদি ফিরে যাই— ইলিয়াস শাহি বংশের শেষের দিকে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের আমলে। তাঁর সাথে মালাধর বসুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি তার বইয়ের ভূমিকায় লিখছেন,
গুন নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥
সত্যরাজ খান হয় হৃদয় নন্দন।
তারে আশীর্বাদ কর যত সাধুজন॥
অর্থাৎ, গৌড়েশ্বর বা বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ তাকে উপাধি দিয়ে সম্মানিত করছেন। হোসাইন শাহের সময় চট্টগ্রামের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর ছেলেকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে রামায়ণ-মহাভারতের কিছু পর্ব অনুবাদ করার জন্য। কসমোপলিটান ধারাতো এই মাটি থেকে এইভাবে জন্মিয়েছে। তারপরে ফোক ধারা একটি বিশাল শক্তিশালী ধারা। সেই ধারাগুলো এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে।
চৈতন্যের বাড়ি তো সিলেটের দক্ষিণ ঢাকায়। তার বাবা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন টোল পন্ডিত। এখন সিলেটের একটি অখ্যাত গ্রামে একটি টোল চালু করলে তো সেটা চলবে না। কারন টোল হল হিন্দুদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে শুধু ব্রাহ্মনের সন্তানরা লেখাপড়ার সুযোগ পেত। তাই তাকে এমন এক জায়গায় বেছে নিতে হয়েছে যেখানে টোল খোলা যাবে। সেজন্য তিনি চলে এলেন নবদ্বীপে। এখন চৈতন্যচরিত কাব্যে বিশেষ করে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’-এর একটি জায়গা আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। যে নবদ্বীপে চৈতন্যের জন্ম সেই নবদ্বীপের বর্ণনাটা আমাকে কসমোপলিটান ধারায় নিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। সেখানে বলা হচ্ছে—
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রীভূবনে নাঞি ।
যহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি ।।
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা ।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা ।।
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে ।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ।।
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায় ।
নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিদ্যারস পায় ।
ভারতের নানা অঞ্চল থেকে নবদ্বীপে লোক সমাগম হচ্ছে এবং সেখানে টোল খুলে বসছেন। এই যে একটি একীভূত করার ব্যাপার সেটা যেমন হিন্দু ধারায় চলেছে তেমন মুসলিম ধারায়ও চলেছে। সুতরাং ধর্ম দিয়ে সেগুলোকে যদি আটকে ফেলি তাহলে আমাদের চিন্তা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। এটাই ছিল বাংলার সহজাত প্রকৃতি। তো সেইভাবে এগুলো বিকাশ লাভ করছে। মোঘল যুগে এসে এই ধারা কিছুটা অব্যাহত থেকেছে। মুসলিম সাহিত্যগুলো প্রধানত সুলতানি আমলের শেষ এবং মোঘল যুগে এগিয়ে গেছে। কেন এগিয়ে গেল? কারণ হিন্দু সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত। সবগুলোর মধ্যে সেই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।আমরা যদি মধ্যযুগের বাংলার এই কসমোপলিটন ধারা বুঝতে চাই তাহলে একটু সরলভাবে না বুঝলে সেই ধারা বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার একটি সমূহ সম্ভাবনা থাকে।