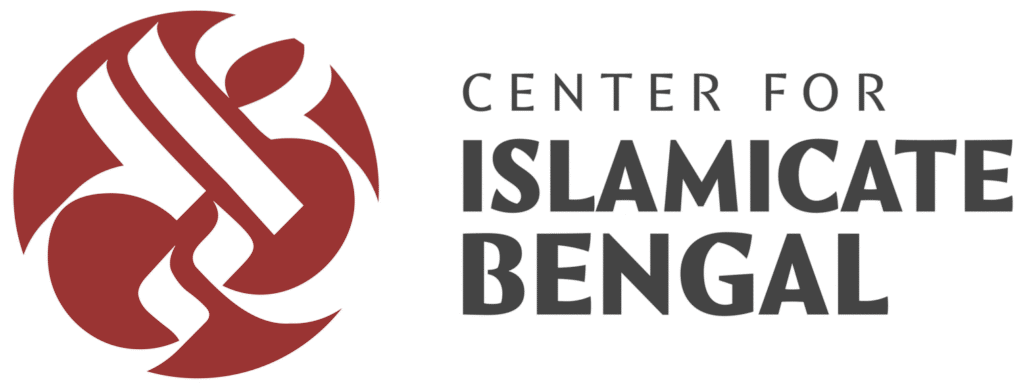প্রথমত, আমরা যখন ইসলামের রাষ্ট্রক্ষমতা কিংবা একই সাথে ধার্মিকতার কথা বলি, তখন এর সত্যিকারের পাটাতন আছে। ফলে সেখান থেকে আমাদের কথা বলতে হয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) পৃথিবীতে কেন এসেছেন; তার আসার প্রয়োজনীয়তা কী ছিল? – অন্যান্য নবীরাও এসেছেন, তিনি কেন এসেছেন? দ্বিতীয়ত, চার্চ এবং রাষ্ট্র যখন আলাদা হয়ে গেছে, তখন পৃথিবীর মধ্যে যে ভারসাম্যটা ছিল, সেটা কতটা নতুনভাবে উদ্ভাবনী জায়গায় রূপ পেয়েছে নাকি উল্টো ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে– সেটা নিয়ে ভাবার দরকার আছে। বর্তমান প্রেক্ষাপট থেকে আমরা যখন মির্জা দেলোয়ার, জামালউদ্দিন আফগানী, মোহাম্মদ আবদুহু প্রমুখ আধুনিক মুসলিম চিন্তকদের কথা বলি তখন প্রশ্ন আসে যে, আমরা তাদের চিন্তা কতটুকু গ্রহণ করতে পারি বা না পারি।
অর্থনীতিতে ‘ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক বিধি’ নামে একটা তত্ত্ব আছে সেখানে বলা হয়ে থাকে যে, পাঁচ শতাংশ আকারের একটি জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ দিলে আনুমানিক সেখানে পাঁচ মণ ধান হবে। এখন যদি আপনি দ্বিগুণ বীজ, সার অন্যান্য উপকরনও দ্বিগুণ করে দেন, তাহলে প্রশ্ন হলো সেখানে কি ১০ মণ ধান হবে? এই তত্ত্বের ভেতরে আশ্চর্য বিষয়টা হলো, কৃষিবিদ ও বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে আমরা যত বেশি বীজ ও সার দেই, উৎপাদন কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়ে না, বরং ধীরে ধীরে কমতে থাকে অর্থাৎ আপনি বীজ, সার, এবং অন্যান্য সব উপকরণ দ্বিগুণভাবে ব্যবহার করেন তবুও উৎপাদন ১০ মণ হবে না, হয়তো হবে সাত মণ। একইভাবে যদি উপকরণগুলো তিন গুণ করেন, তখনও ব্যাপারটা এমন হবে না যে ১৫ মণ ধান হবে, হয়তো ৯ মণ হবে। এই ভিত্তি থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ে হিসাব করা হয়েছিল বলা হতো, আমাদের জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, কৃষিজমি তো সে অনুপাতে বাড়ছে না; ফলে এক সময় দেশের মানুষ অভুক্ত থাকবে তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
প্রথমে বলা হলো দুইটি সন্তান নিতে হবে। পরে বলা হলো—না, একটি সন্তানই নিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে, তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা। পরবর্তীতে যখন ইরি ধান এবং হাইব্রিড প্রজাতির নতুন ধান এলো, তখন দেখা গেল, যে ২০ শতক জমিতে আমি ছোটবেলায় দেখতাম পাঁচ মণ কিংবা আট মণ ধান হতো, সেখানে এখন ২০–২২ মণ পর্যন্ত ধান হচ্ছে। প্রশ্ন হলো,তাহলে কী ঘটল? আমাদের আগের তথ্য ছিল দ্বিগুণ সার দিতে হবে। অথচ এখানে দ্বিগুণ সার দিতে হয়নি, এমনও নয় যে দ্বিগুণ যত্ন নিতে হয়েছে বরং মূল পরিবর্তন এসেছে প্রজাতি বদলানোর মাধ্যমে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, অনেক সময় যে তত্ত্ব বা হিসাব সামনে আসে, বাস্তবে ঘটনা সব সময় সেই হিসাবমতো ঘটে না।
আরেকটা উদাহরণ নিলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের যিনি গভর্নর হিসাবে আছেন, তার একটি সাক্ষাৎকার দেখলাম। সেখানে তিনি বলছিলেন যে, সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান একটি নতুন ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন যে, মানুষকে আরও বেশি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে হবে। সে জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ দিতে হবে, যেন বিপুল সংখ্যক মানুষ ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারে যখন ব্যাংক একাউন্ট বেশি হবে, তখন মানুষ ব্যাংকিং লেনদেনে বেশি আগ্রহী হবে এবং বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এক ধরনের স্ফুরণ ঘটবে। যেহেতু তখন ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটে ভুগছিল কিন্তু বাস্তবে কী ঘটলো? প্রায় দেড় কোটির মতো ব্যাংক একাউন্ট খোলা হলো, কিন্তু সেই একাউন্টগুলোর বড় অংশ এখন নিষ্ক্রিয়, কাজে লাগছে না। কারণ, এর মধ্যেই দেশে নতুন প্রযুক্তি,মোবাইল ব্যাংকিং চলে এসেছে মানুষের সবার হাতে হাতে মোবাইল ফোন চলে আসায় ১০ টাকা দিয়ে আলাদা ব্যাংক একাউন্ট খোলার প্রয়োজন থাকে নি। এখন মানুষ তার বিকাশ, নগদ ইত্যাদি মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট দিয়েই নিজের সব ধরনের ব্যাংকিং লেনদেন সারছে। এখন প্রশ্ন হলো, দেড় কোটির মতো যে ব্যাংক একাউন্ট খোলা হলো, এগুলো কি প্রায় নষ্ট হয়ে গেল না?
এই উদাহরণগুলো আনার উদ্দেশ্য হলো, মির্জা দেলোয়ার সম্পর্কে যখন আমরা পড়ব তখন এই ধরনের বাস্তবতা আর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট আমাদের মাথায় রাখতে হবে। বলা হয় ঔপনিবেশিক আমলে বিদ্যমান তিনটি শ্রেণী থাকার কথা— রক্ষণশীল, সংস্কারবাদী এবং বিপ্লবী। বর্তমান সময়ে, যদি আপনি শুধু “ইসলামিস্ট”দের মধ্যে তাকালেই তিনটি ধারা দেখা যাবে। একটি পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়, একটি সংস্কারবাদী, আরেকটি জিহাদী ধারা। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় আমরা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যাব? আমাদের আগের যে তত্ত্বগুলো ছিল, সেগুলোর সাথে এখনকার বাস্তবতা মিলছে কি না, সেটাও ভাবতে হবে।
যখন আমরা জামালউদ্দিন আফগানী বা মোহাম্মদ আব্দুহর কথা বলি অথবা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আবুল ফজল, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাশিম কিংবা সর্বশেষ শেখ মুজিবুর রহমানের মতো ব্যক্তিদের চিন্তা দেখি তখন দেখা যায়—তাদের সবার মধ্যেই একটা সাধারণ ভাবনা ছিল, মুসলিম সমাজ কীভাবে সমৃদ্ধ হবে, কীভাবে উন্নত হবে, কীভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এমন এক অবস্থানে যাবে যাতে অমুসলিম, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের সাথে তারা টিকে থাকার ও প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু আমরা একটু পরের পর্যায়ে এসে দেখি, এই চিন্তার প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো দিকে গিয়েছে। অর্থাৎ, যদি আমাদের লক্ষ্য হয় মুসলিম সমাজের উত্তরণ, মুসলিম সমাজকে সমৃদ্ধ করা, তাহলে হওয়ার কথা ছিল যারা বেশি মুসলিম, যারা বেশি ইসলামের চর্চা করে, তাদের আমরা বেশি সম্মান দেব, তাদেরকে সামনে তুলে আনব। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, ‘সমৃদ্ধি’র নামে অনেকেই এত বেশি সেকুলার, এত বেশি পশ্চিমা বা ইউরোপীয় নীতি মূল্যবোধ গ্রহণ করেছেন যে ইসলামের মূল মূল্যবোধ থেকে ধীরে ধীরে সরে গেছেন।
ফলে ইসলামের কোর ভ্যালুগুলো রক্ষা করার জন্য আবার নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তখন আমরা দেখি, আগে থেকেই মাদ্রাসা থাকা সত্ত্বেও নতুন ধরনের মাদ্রাসার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এই নতুন মাদ্রাসাগুলো আবার মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যে আগের মুসলিম বনাম অমুসলিম’ বিভাজন ছাড়িয়ে নতুন এক বাইনারি তৈরি হয়েছে—ইসলামিস্ট বনাম নন–ইসলামিস্ট, কিংবা ইসলামিস্ট বনাম সেকুলার। যারা ইসলামের কোর ভ্যালুকে গুরুত্ব দিয়ে ধর্ম নিয়ে ভাবে, তারা সেকুলারদের থেকে নিজেদের এত দূরে সরিয়ে রেখেছে যেন ওটা এক ধরনের ‘অচ্ছুত’ গোষ্ঠী। অন্যদিকে সেকুলাররাও তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছে, অনেকটা সেই অর্থে যেভাবে এক সময় নিম্নবর্ণের নমশূদ্র হিন্দুদেরকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেখা হতো। এভাবে সমাজ বাস্তবতায় যা ঘটছে, তা হলো,আমরা যে পথকে উন্নয়নের পথ ভেবে ভাবছিলাম, যে ধারণা করছিলাম মুসলিম সমাজ বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো একটু একটু করে এগিয়ে যাবে, বাস্তবে তা অনেক সময় উল্টো দিকে গেছে, আমরা আরও পশ্চাৎমুখী হয়েছি।
আমরা যখন ইসলাম ও রাষ্ট্র, ইসলাম ও উন্নয়ন, কিংবা ইসলাম ও বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করি, তখন বাংলাদেশের মানুষের একটা বড় অংশ প্রথমেই আঙুল তোলে মাদ্রাসার দিকে, কেন মাদ্রাসায় বিজ্ঞান পড়ানো হয় না ইত্যাদি। এটা বাস্তব একটা প্রশ্ন, কিন্তু আরেকটা প্রশ্নও আছে যেটা করা উচিত। যেখানে বিজ্ঞান পড়ানো হয়, তারা কতটা বাস্তব উন্নতি করতে পেরেছে? যে উন্নয়নটা না হওয়ার জন্য মাদ্রাসাকে একমাত্র দায়ী করা হয়, বাস্তবে কি সেটা ঠিক? মাদ্রাসা তো রাষ্ট্রের বড় বড় প্রযুক্তিগত প্রকল্প আটকে দেয়নি বাংলাদেশের কোথায় স্যাটেলাইট যাবে, তা নিয়ে তো কোনো আলেম বলেছেন যে, ‘না, আপনি স্যাটেলাইট পাঠাতে পারবেন না, এটা বিজ্ঞানের কারণে ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক’? বরং সমস্যা অন্য জায়গায় হয়েছে যারা নিজেকে সেকুলার ধারার, আধুনিক ধারার বা বিজ্ঞানমনস্ক বলে পরিচয় দেন, তারা ক্ষমতা ও সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে এমনভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছেন যে, নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক আস্থাই নষ্ট হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের একটি স্যাটেলাইটের প্রাথমিক হিসাব ছিল চার মিলিয়ন ডলার, পরে সেটা ৪০ মিলিয়ন হয়ে গেল বড় বড় উন্নয়ন বাজেটের হাজার–হাজার কোটি টাকা লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে, এবং এগুলো করেছে মাদ্রাসাশ্রেণি নয়, বরং মূলধারার, ‘বিজ্ঞানমনস্ক’ বা আধুনিক বলে পরিচিত গোষ্ঠী। প্রশ্ন হলো, যদি এই লুটপাট, পাচার, দুর্নীতিগুলো না হতো, তাহলে কি বাঙালি মুসলমান বা সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজ আরও সমৃদ্ধ হতো না? অবশ্যই হতো।
মূল সমস্যা হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা। আমরা যখন ইউরোপীয়দের দিকে প্রবল মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়েছি, তখন ধীরে ধীরে আমাদের নিজের কোর ভ্যালুগুলো ভেঙে গেছে। যে জায়গায় ইসলামের মূল মূল্যবোধ থাকার কথা ছিল, সেখান থেকেই আমরা সরে গেছে। এই প্রসঙ্গে আমি মির্জা দেলোয়ারের সুদের উদাহরণটা টানব। তিনি বলেছিলেন, মুসলিম সমাজে সুদকে কোনো সীমার মধ্যে সহনীয় করা যায় কি না, বা অন্তত একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রেখে দেখা যায় কি না। প্রশ্ন হলো, আমরা কি সত্যিই কোনো সীমার মধ্যে সুদকে আটকে রাখতে পেরেছি? বরং সুদের গ্রাস এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে বাড়তে সুদই মানুষকে গিলে খাচ্ছে। আমরা শুনি, কোনো এক বৃদ্ধা কোনো এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছেন, বারবার ঋণ নিয়ে আবার পরিশোধও করছেন, কিন্তু ঋণের আসল টাকা তিনি কখনোই নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারছেন না, সবই কিস্তি পরিশোধে চলে যাচ্ছে একপর্যায়ে তার হাতে টাকা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঋণ শেষ হয়নি গ্রামের বহু মানুষ এই সুদের ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে—এটা আমাদের বাস্তবতা।
এখন প্রশ্ন, এই সব তথ্য ও বাস্তবতাকে আমরা কোন পর্যায় পর্যন্ত গ্রহণ করব, আর কোন পর্যায়ে গিয়ে ‘না, এখানে আমাদের থামা দরকার’ বলব—এই ভারসাম্যটা আমাদের বজায় রাখা উচিত ছিল। যেসব তাত্ত্বিক পরে এসেছেন হোক সেটা মির্জা দেলোয়ার বা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের লেখক তাদের অনেক-ই ইসলামের কোর ভ্যালুজ থেকে সরে এসেছে, যেখানে তাদের চিন্তা শেষ পর্যন্ত মানুষ ও সমাজের জন্য বিধ্বংসী পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ তা’আলা নিজেই বলেছেন, সুদ কীভাবে মানবসমাজকে ধ্বংস করে—আমরা সেই ধ্বংসের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যেই এখন আছি।
মির্জা দেলোয়ারের প্রসঙ্গে বারবার যে কথা আসছে—তিনি চেয়েছিলেন, মুসলমান সমাজে কিছু ক্ষেত্রে ইজতিহাদ আসুক যেমন, সুদ, বিবাহ, এবং বহু বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে। প্রথম প্রশ্ন হলো, সত্যিই কি এসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রয়োজন ছিল? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, ইজতিহাদ তো এমন জিনিস নয়, যেটা যে কেউ নিজের ইচ্ছেমতো করে ফেলতে পারে। বরং, এর জন্য কিছু ধর্মীয় শর্ত, নৈতিক যোগ্যতা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের পূর্বশর্ত আছে। ইজতিহাদ করার আগে দেখতে হবে সে ধর্মীয় শিক্ষায় কতদূর গিয়েছে, শাস্ত্রীয়ভাবে কতটা প্রস্তুত।
আমরা যখন এই সব শর্তকে প্রায় অগ্রাহ্য করে ইজতিহাদের কথা বলতে শুরু করি, তখন বাস্তবে যা হয়, তা হলো—আমি ইজতিহাদ করি ইসলামের ভেতর থেকে নয়, বরং আগে থেকে নিজের মতো করে ঠিক করা একটি অবস্থান থেকে, যেখানে আমি ইউরোপীয় ভ্যালু এবং ইসলামের কিছু অংশকে মিলিয়ে একটা নতুন কাঠামো বানাতে চাই। এর উদাহরণ মির্জা দেলোয়ার নিজেই। তিনি বলেছিলেন, বহু বিবাহ মুসলিম সমাজে সমস্যা তৈরি করছে, কারণ এতে জমি বণ্টন, সম্পদ বণ্টন, পরিবার–ব্যবস্থা সব জায়গায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এখানে যে মূল্যবোধটা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল, সেটা হলো কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ বহু বিবাহের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার (ইনসাফ) নিশ্চিত করা। কোরআন বলেছে, যদি তুমি স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করতে না পারো, তাহলে তোমার জন্য একটিই যথেষ্ট। রাষ্ট্র চাইলে এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারতো—যেহেতু বাস্তবে ইনসাফ করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই একাধিক বিবাহের অনুমতি বাস্তবে প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে আসবে। কিন্তু সেটা না করে, যখন আমরা বলি, ‘বহু বিবাহ সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে’, তখন অনেক জায়গায় নতুন সমস্যা তৈরি হয়।
এরই একটি উদাহরণ—সমাজে প্রচুর বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা বা বয়স্কা নারী আছেন, কিন্তু তাদের জন্য উপযুক্ত বর নেই। সমাজে এক ধরনের ইমব্যালান্স তৈরি হয়েছে যে, কম বয়সী ছেলেরা অনেক ক্ষেত্রে বেশি বয়সী নারীকে বিয়ে করতে চায় না। অথচ ইসলাম এটাকে নিরুৎসাহিত করে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহিতও করেছে। অনেক মেয়ে হয়তো শারীরিকভাবে অক্ষম, প্রতিবন্ধী, বা সামাজিকভাবে খুব দুর্বল; তাদেরকে বিয়ে করার মতো কেউ সামনে আসে না। এই ভারসাম্যহীনতা আমরা কীভাবে সামাল দিব? এই ম্যানেজমেন্টের অনেক দিক আসলে ধর্মের কোর ভ্যালুর মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু আমরা সে সব ব্যবহার করি না। একইভাবে, সুদের ব্যাপারে আমরা চাইলে বিকল্প সমাধানের দিকে যেতে পারতাম। সেই জায়গায় না গিয়ে আমরা সুদকে রাষ্ট্রের মূলধারার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এখন প্রচলিত ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংক—দুটোই প্রায় একই কাঠামোর ভেতরে চলে গেছে। কিন্তু আমাদের সমাজে আগে একটি প্রথা ছিল—ফসল ঘরে ওঠার সময় মানুষ মসজিদে বা মহল্লায় একটি গুদামে শস্য জমা রাখত। কেউ প্রয়োজন হলে সেই গুদাম থেকে শস্য ঋণ হিসেবে নিতে পারত, পরে তা ফেরত দিত—এসব ছিল সামাজিক সমাধান। আমরা সেসব সামাজিক বিকল্প শক্তিশালী না করে, যখন সুদকে ‘সহনশীল’ করার কথা বলতে থাকি, তখন সুদ ধীরে ধীরে আকর্ষণীয় এক মোহের মতো মানুষের ভেতরে ঢুকে যায়।
মানুষ দেখে, কোনো জবাবদিহিতা ছাড়াই তার টাকা একটু একটু করে বাড়ছে, অল্প অল্প করে সেই টাকা পাঁচ লাখে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর আরও বাড়ে তখন সে এই চক্র থেকে বের হতে চায় না, বা পারেও না—কারণ মানুষের মন স্বভাবতই লোভ ও মন্দ কাজের দিকে টান অনুভব করে। এই কারণে সমাজের নেতৃত্বে যারা থাকেন, তাদের সামনে দায়িত্ব ছিল—ইসলামী ভ্যালুর আলোকে কীভাবে এই সুদের সমস্যার সামাজিক সমাধান বের করা যায়। যদি সত্যিই এমন হতো যে, ইসলামের ভেতরে এ নিয়ে কোনো কথা নেই, কোনো নির্দেশ নেই, তাহলে বলতাম,এ নিয়ে ইসলামের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন—ইসলামে শুধু কিছু বিষয় স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এর বাইরে মানুষের জন্য অনেক বিস্তৃত হালালের পরিসর উন্মুক্ত আছে। ফলে বিজ্ঞানের জায়গায় মুসলমানরা কোথায় যাবে, সমৃদ্ধির জায়গায় কতদূর যাবে?—এগুলো নিয়ে ইসলামের মৌলিক কোনো বাধা নেই। সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মুসলমানরা সব সময় উন্নয়ন, জ্ঞান ও সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়েই এসেছে। মুসলিম শাসনকালগুলোতে আমরা দেখি—ইউরোপিয়ানরাই চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্য মুসলিম বিশ্বের দিকে আসত। ‘দ্য ফিজিশিয়ান’– বইয়ে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় ছাত্ররা মুসলিম চিকিৎসকদের কাছে শিখতে আসছে অর্থাৎ, এক সময় মুসলমানদেরই ভ্যালু ও জ্ঞান অন্যদেরকে আকৃষ্ট করত।
এখন যদি প্রশ্ন করেন, মুসলমানরা এই ভ্যালুগুলো কোথা থেকে পেয়েছে? দেখবেন, মুসলমানরাও এক সময় অন্য সভ্যতা থেকে জ্ঞান নিয়েছে যেমন, ইমাম গাজ্জালী, ইবনে সিনা, ওমর খৈয়াম—অনেকেই গ্রিক দার্শনিকদের কাছ থেকে জ্ঞানের রসদ নিয়েছেন, গ্রিক দর্শনের অনেক কিছু নিজেদের ভেতরে গ্রহণ করেছেন এগুলো কোনো সমস্যা ছিল না। সুতরাং, মির্জা দেলোয়ার বা তার আগের কিংবা পরের চিন্তকরা—তারা যা–ই করেছেন, আমার মনে হয় ধর্মের ভেতরে নতুন করে ‘ইজতিহাদ’ নাম দিয়ে অনেক কিছুকে ঢুকিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল না। বরং দরকার ছিল, ধর্মের ভ্যালু ও নৈতিক কাঠামোকে নিয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা, গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা, এবং মুসলিম সমাজের বাস্তব উত্তরণের পথ নিয়ে কাজ করা। কিন্তু এই উত্তরণের মৌলিক প্রশ্নগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এড্রেস করিনি।
বর্তমানে দেখা যায় যে, ইউরোপ বা আমেরিকায় মুসলিম কমিউনিটিগুলোর মধ্যে আরেক ধরনের বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। তারা তাদের সন্তানদের নৈতিকতা শেখানোর দায়–দায়িত্ব প্রায় পুরোপুরি ইমামের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এটা কোনো সমাজের উন্নয়ন বা মূল্যবোধ রক্ষার টেকসই উপায় হতে পারে না। আমাদের সমাজেও একই ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। মা–বাবা ভাবছেন, স্কুল মূল্যবোধ শেখাবে; স্কুলের মানুষ ভাবছে, পরিবার মূল্যবোধ শেখাবে ফলে প্রশ্ন থাকে—মূল্যবোধ আসলে কে শেখাবে? এই জায়গায় আমাদের একটা বড় কনফিউশন তৈরি হয়েছে। তাই দরকার ছিল যে, ইসলামের কোর ভ্যালুগুলোর দিকে ফিরে দেখা—কোন মূল্যবোধগুলো ইসলামের কেন্দ্রীয় শিক্ষা, সেগুলো পরিবার, শিক্ষা এবং সমাজ–পর্যায়ে কীভাবে স্থাপন করা যায়
আমাদের দেশে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের ঘটনাকে অনেকে পাশাপাশি বা তুলনামূলকভাবে দেখতে চান আবার কেউ কেউ শাহবাগের সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নতুন করে শুরু করা, পুনর্বিবেচনা করা—এসব নিয়ে কথা বলেন। কোনো মুসলিমই ন্যায়সঙ্গত বিচারের বিরুদ্ধে থাকতে পারে না যে অপরাধ করেছে, তার বিচার হওয়া উচিত এটা মৌলিক নীতি। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়—বিচারের প্রক্রিয়ার ভেতরে যখন দুর্নীতি ঢুকে পড়ে যেখানে এমন সাক্ষী হাজির করা হয়, যে সাক্ষী বাস্তবে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্তই নয়, বা অস্তিত্বই নেই; আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়, কাদের বিচার করতেই হবে; একই সাথে একটি সংস্কৃতি তৈরি করা হয় যে, এখানে নাকি সবচেয়ে বড় বাধা ‘ইসলাম’। ফলে আপনাকে এমন একটি কমিউনিটি দরকার হয়, যারা শাহবাগে এসে বলবে, ‘এখানে ইসলাম নেই, এখানে হুজুরদের প্রভাব আছে, তাই তাদের বিরোধিতা করতে হবে’। এইভাবে লক্ষ্য হয়ে যায়—কিছু নির্দিষ্ট মানুষকে ফাঁসি দিতেই হবে, অপরাধ–বিচার নয়, বরং ‘জুডিশিয়াল কিলিং’ এটা না করে, যদি সত্যিকারের অপরাধীদের চিনে, ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ–প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার করা হতো, তাহলে বাঙালি মুসলমান সমাজ, হুজুর সমাজ, কিংবা হেফাজত- এর মতো উত্থান কখনোই এভাবে তৈরি হতো না, অন্তত এ তীব্রতায় হতো না। সমস্যা হয়েছে তখনই, যখন আন্দোলনের যথেষ্ট সামাজিক সমর্থন না পেয়ে, তাকে ধর্মের সাথে গুলিয়ে দিয়ে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মনে হয়েছে, ‘সমস্যাটা ধর্মের’ বাস্তবে এটা ধর্মের কোর ভ্যালুর সম্পর্কে না বুঝাবুঝির ফল।
একদিকে কালচারাল পলিটিক্সের মাধ্যমে ধার্মিকদের ক্রমাগত আঘাত করা হয়েছে; অন্যদিকে কেউ কেউ চেয়েছেন ধার্মিক শ্রেণীকেই পুরোপুরি মুছে দিতে, আবার কেউ ধার্মিকদের কিছু বিচ্ছিন্ন, ভুল আচরণকে পুরো ধর্মের নামে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন। যেমন, কেউ যদি বলে, ‘দোরা মারা মানেই ধর্ম’, এটা স্পষ্টতই ভুল ধার্মিকদের কিছু আচরণকে পুরো ধর্ম বলে চালানো যায় না ।
সুতরাং, যখন আমরা কোনো সমাজের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি বা উত্তরণের জন্য ধর্মের ভূমিকা বিচার করব, তখন আগে আমাদের ধর্মকে পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং ইসলামের কোর ভ্যালুগুলো স্পষ্টভাবে জানতে হবে—কোনটা আসলেই ধর্মের অংশ, আর কোনটা নয়। যদি কোনো বিষয় ধর্মে স্পষ্টভাবে না থাকে, তাহলে সেটাকে নিয়ে ‘ধর্ম সমস্যার উৎস’—এভাবে বলা যাবে না আর যদি কোনো বিষয় ধর্মে স্পষ্টভাবে থাকে, তাহলে দেখতে হবে, বর্তমান বাস্তবতার সাথে তার সংঘাত কোথায়, সেটা কি সত্যিই মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী, নাকি আমরা ভুলভাবে বুঝছি। যদি দেখা যায়, ইসলামের মূল মূল্যবোধগুলো বাস্তবতার তুলনায় সত্যিই উত্তম, তাহলে আমরা সেটা কেন ছেড়ে দেব? আর যদি কোথাও মনে হয়, আমাদের বোঝাপড়ায় সমস্যা আছে, তখন ধার্মিক সমাজের সাথে বসে আলোচনা করে—ইখতেলাফের মধ্যকার বিভিন্ন মতের ভেতর থেকে উপযুক্ত সমাধান বেছে নেওয়ার পথ খুঁজতে হবে। ইসলামের ভেতরে বহু ইখতেলাফি মত আছে, যার মাধ্যমে নানা প্রসঙ্গে ফিকহি সমাধান বের করা যায়।